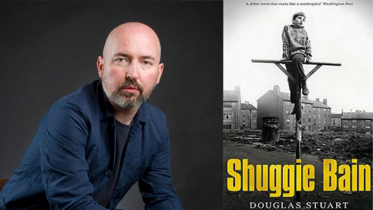‘পেছন ফিরে তাকাই যখন’
প্রকাশিত : ২০:৩২, ১০ মে ২০১৮ | আপডেট: ২০:৩৭, ১০ মে ২০১৮

আজ থেকে চুয়ান্ন বছর আগের কথা। কেমন করে যে এতগুলো বছর পার হয়ে গেল, তা ভাবতেও অবাক লাগছে।আব্বার রেলওয়েতে চাকরির সুবাদে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলার মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল এবং তাদের সামাজিক আচার-আচরণ, সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছিলাম।
ওই সময়টাই ছিল এমন। শায়েস্তাগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগে যমুনা নদীর তীর ঘেঁষা শহর সরিষাবাড়ী গার্লস হাইস্কুলে পড়তাম। তখনও দেখেছি মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকদের অনীহা ছিল। আর এ কারণেই স্কুলের চারজন আয়া সকালে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রীদের নিয়ে স্কুলে আসত; আবার স্কুলছুটির পর বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিত। ১৯৬৩ সালে আব্বা শায়েস্তাগঞ্জে বদলি হলেন। বদলির কারণে আব্বার আর আমাদের মন ভীষণ খারাপ ছিল। বিশেষ করে আমার। কারণ শায়েস্তাগঞ্জে তখন মাধ্যমিক স্তরের কোনো গার্লস স্কুল ছিল না। ইচ্ছে না থাকা সত্তে¡ও আমাদের নিয়ে ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে আব্বা চলে এলেন শায়েস্তাগঞ্জে।
এখানে এসেই আব্বার সঙ্গে গিয়ে আমি আর আমার দুই ভাই শায়েস্তাগঞ্জ স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে আমি অষ্টম শ্রেণিতে এবং দুই ভাই ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হই। প্রথম প্রথম ছেলেদের স্কুলে পড়তে বেশ অস্বস্তিতে ভুগছিলাম। নতুন জায়গায় কিছুটা নতুনত্ব ছিল বৈকি! কিন্তু নিজেকে যেন সহজে খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না। তবে ধীরে ধীরে সব ঠিক হতে লাগল। স্কুলটি কিন্তু আমার প্রথম দেখাতেই ভালো লেগেছিল। ছায়া সুনিবিড়। কোথাও কোনো কোলাহল নেই। শান্ত পরিবেশ। স্কুলের পূর্বদিকে বহমান খোয়াই নদী, উত্তরে শায়েস্তাগঞ্জ-সিলেট রেললাইন সমান্তরাল চলার অনুপম চিত্র ও পশ্চিম পাশেই বিশাল খেলার মাঠ। তাছাড়া রেল স্টেশন ও বাজার থেকে প্রায় এক মাইল দূরত্বে সুন্দর শান্ত পরিবেশ। বৃহদাকারের হৃষ্টপুষ্ট অসংখ্য ডালপালাসমৃদ্ধ শিরিষ গাছগুলোর ছায়া যেন আরো শীতল ও শান্ত করে রেখেছিল স্কুলের পরিবেশ।
প্রায় এক হাজার ছাত্রের মধ্যে মাত্র দশ-বারো জন ছাত্রী ছিলাম আমরা। আমাদের জন্য আলাদা বসার কোনো রুম ছিল না। টিচার্স কমনরুমেই তিন-চারটি বেঞ্চে আমরা বসতাম। তাই বলে আমাদের জন্য শিক্ষকদের কোনো অসুবিধা হতো বলে আজো মনে করি না। ক্লাসে যাওয়ার সময় আমরা স্যারদের পেছনে পেছনে যেতাম। ক্লাস শেষে আমরা আবার আমাদের জায়গায় এসে চুপচাপ বসে থাকতাম। অষ্টম শ্রেণিতে একশ’র মতো ছাত্র ছিল আর আমরা ছাত্রী ছিলাম মাত্র আটজন। বার্ষিক পরীক্ষার পর মাত্র দুজন ছাত্রী আমি আর হেনা প্রমোশন পেয়ে নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হলাম। বাকি ছয়জন ঝরে পড়ল। তখনকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি তো আর এখনকার মতো ছিল না। মেয়েদের শিক্ষার হার ছিল খুবই নগণ্য। তাছাড়া ছিল সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও বাধানিষেধ। লেখাপড়া করার ইচ্ছা সবার; কিন্তু সামাজিক বাধানিষেধের কারণে তা সম্ভব হতো না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। মুসলিম পরিবারের মেয়েদের স্কুলে লেখাপড়া করাটাকে মেনে নেওয়ার মনমানসিকতা ছিল না তখনকার সমাজে। কিছু কিছু অভিভাবক মনে করতেন প্রাইমারি পাস করে চিঠিপত্র পড়তে ও লিখতে পারলেই যথেষ্ট। আবার কেউ কেউ সেটাও মেনে নিতেন না। মেয়েরাও যে উচ্চশিক্ষিত হয়ে চাকরি করে ছেলেদের সমপর্যায়ে বা পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে সেই চিন্তা কোনো কোনো অভিভাবকের মনেও হয়নি।
এছাড়া ছিল বাল্যবিয়ের প্রকোপ। বারো-তেরো বছর হলেই বিয়ের কাজটা শেষ করে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন অভিভাবকরা। অনেকের ধারণা ছিল, মেয়েদের বেশি পড়ালেখার প্রয়োজন নেই। শায়েস্তাগঞ্জ স্কুলে আমার তিন বছরের অভিজ্ঞতা থেকে যতটুকু দেখেছি, তখনকার ছেলেরা অত্যন্ত সভ্য, ভদ্র ও মার্জিত ছিল। সবার একমাত্র লক্ষ্যই ছিল লেখাপড়া শিখে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা। যতদিন এ স্কুলে পড়াশোনা করেছি, এ সময়ের মধ্যে আমরা কোনোদিন কোনো ছাত্রের সঙ্গে কথা বলিনি। এখন কি এটা সম্ভব? অথচ আমরা অনেকেই একই পথে স্কুলে আসা-যাওয়া করতাম। আমাদের শিক্ষকরাও তাদের পেশাকে নেশা হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। তাদের যোগ্যতা দিয়েই ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন। তাঁরা আমাদের স্নেহ, ভালোবাসা, শাসন, আদেশ, উপদেশ দিয়ে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। দু-তিনজন স্যার ছাড়া বাকি সবাই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। আমরা তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি। আমরাও মরণসমুদ্রের বেলাভ‚মিতে দাঁড়িয়ে আছি। যতদিন বেঁচে থাকব, আদর্শ মানুষ হিসেবে যেন বেঁচে থাকি।
সবার ভালোবাসা ও দোয়া প্রত্যাশা করি।
লেখক: ১৯৬৬ ব্যাচের শিক্ষার্থী