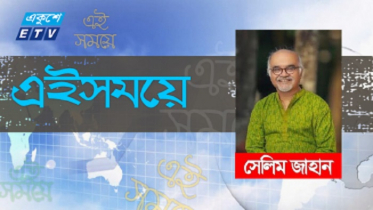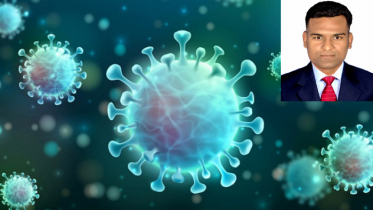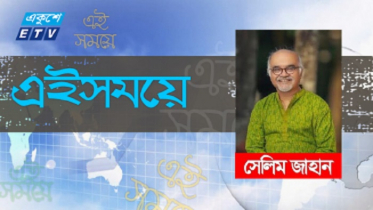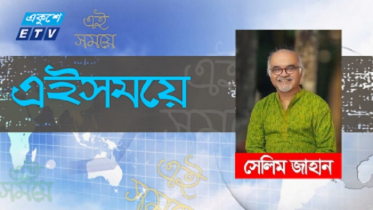নামে কী বা আসে যায়
প্রকাশিত : ০০:০৭, ২৭ মার্চ ২০১৮ | আপডেট: ১০:২৮, ৪ এপ্রিল ২০১৮

গোলাপকে যে নামেই ডাকুন, সে সুগন্ধ বিলাবেই, আর গোবরকে গন্ধরাজ বলে যতই ঘাঁটাঘাঁটি করুন, তাতে খুশবু বেরোবে না। তার মানে, নামের কারণে কোনো বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণাগুণের হেরফের হয় না। চুনকে দই মনে করে খেলেও মুখ ঠিকই পোড়াবে, রসগোল্লার নাম বদলিয়ে তেঁতুল রাখতে পারেন, কিন্তু এতে তার রসালো মিষ্টিমধুর স্বাদে কোনো তারতম্য হবে না।
মানুষের নামের বেলাও কি এই সহজ-সরল নিয়ম খাটে? উত্তর - ‘হ্যাঁ’ এবং ‘না’ দু’টোই হতে পারে। নামে মানুষের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও গুণাবলীতে এদিক-সেদিক হয় কিনা জানি না, তবে এটা জানি, আদম সন্তানের নাম যা ইচ্ছে তা রাখা যায় না। এটা মোটামুটি সর্বজনস্বীকৃত যে, ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে, মা-বাবার ওপর তার প্রথম দাবি - তার জন্য একটি সুন্দর অর্থপূর্ণ নাম ঠিক করা।
অনেক পিতা-মাতা আপন সন্তানের প্রতি এই সামান্য দায়িত্বটুকুও সঠিকভাবে পালন করতে পারেন না। ঊনিশ শ’ আশি দশকের শেষ অথবা নব্বই-এর গোড়ার দিকে আমেরিকার ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের ‘আরবানা-শ্যাম্পেইন’ শহরে আমার পরিচয় হয়েছিল এক সুশিক্ষিত তরুণ বাংলাদেশি দম্পতির সাথে। তাদের ৫/৬ বছরের একটি মেয়ে ছিল। একদিন এক সামাজিক জমায়েতে আমি মায়ের কাছে মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি অত্যন্ত কাতর স্বরে অনুনয়-বিনয় করে বললেন, ‘ভাই, আর বলবেন না, অর্থটা ভালো নয়’। আমি বললাম, কেন, কী হয়েছে? তিনি কাঁদো কাঁদো স্বরে উত্তর দিলেন, ‘আমার মেয়ের নাম ‘অরি’, আপনারা জানেন, ‘অরি’ মানে শত্রু!’ সেদিন ওই মা-বাবার অনুতাপ ও আফসোস দেখে আমার খুব খারাপ লেগেছিল, তথাপি এ রকম একটি স্পর্শকাতর ও ব্যক্তিগত বিষয়ে আমি আর নাক গলাতে যাইনি। এত দিনে নিশ্চয়ই ‘অরি’ আর ‘অরি’ নেই, একটি সুন্দর নতুন নামের অধিকারিণী হয়ে গেছে। ‘অরি’-র মা-বাবাও আর ‘ওয়ারি’ করছেন না, স্বস্তিতে আছেন। অভিভাবকরা তার নামের ব্যাপারে অসাবধানতাবশত যে ভুল করেছিলেন, ‘অরি’ মা হলে তার সন্তানের প্রতি নিশ্চয়ই ওই ভুলটি করবে না।
কেউ কেউ আবার অজ্ঞতা, অর্বাচীনতা ও বুদ্ধিবিবেচনার অভাবেও উল্টোপাল্টা নাম রাখেন। উদাহরণ দিতে গিয়ে এবার ষাটের দশকে ফিরে যেতে হচ্ছে। আমাদের ‘বড়লেখা’ বাজারের একমাত্র মুচি ‘শ্রী গোবিন্দ’ অথবা তার বড় ছেলে ‘রাজুয়া’ যখন তাদের বাড়ির সামনের বেড়াবিহীন ছনের দু’চালা দোকানঘরে মটির ধুলোয় বস্তা বিছিয়ে বসে জুতো সেলাই করতেন তখন দেখতাম তাদের আশেপাশে ‘রাজুয়া’-র ছোট ছোট দুই বোন ঘুর ঘুর করত - তাদের এক জনের নাম ছিল ‘পাইয়া’ আরেক জনের নাম ‘দেড়িয়া’। এমনও শুনেছি, মা-বাবা দুই সন্তানের নাম রেখেছেন যথাক্রমে - ‘এক কড়া’ ও ‘দুই কড়া’। মাহবুবের কাছে শোনা, তাদের প্রতিবেশী দুই ভাই ছিলেন - এক জন হলেন ‘মড়া’ অন্য জন ‘গড়া’। ‘মড়া’র দুই ছেলে - ‘নেউলা’ ও ‘টলা’। একই জায়গায় আরেক উদ্ভট নামধারীর নাম ছিল - ‘ভিঙ্গুল’ (শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলে ‘ভীমরুল)। মাহবুবের সাথে সম্প্রতি ইংল্যান্ডে পরিচয় হয়েছে এক বাংলাদেশি পরিবারের। তাদের চার ছেলে - ‘ফাহিম’, ‘রাহিম’, ‘করিম’ ও ‘রাজিম’। ‘রাজিম’ শব্দের অর্থ ‘অভিশপ্ত’, ‘বিতাড়িত’। এই শব্দটি শয়তান বা ইবলিসের বিশেষণ হিসেবে বিশেষভাবে সুপরিচিত। বলুন তো, এ সব নামের কি কোনো মানে হয়! যে সব অভিভাবক আপন ছেলেমেয়ের জন্য এ জাতীয় নাম বাছাই করেন তাদের জন্য করুণা বর্ষণ করা ছাড়া আর কি কিছু করার আছে? তবে তাদেরকে আমি দোষারোপও করি না। অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অসচেতনতার কারণে মানব জীবনের সূক্ষ্ন অনুভূতির স্পর্শকাতরতায় তারা একেবারেই গাফেল। তাদের ধারণা, একজন মানুষকে আরেক জন মানুষ থেকে আলাদাভাবে সনাক্ত করার জন্য ‘আদা’, ‘গদা’ জাতীয় একটা নাম হলেই তো হলো, এ নিয়ে এত ভাবনাচিন্তার দরকার কী। নামের যে একটি সুন্দর অর্থ এবং নাম যে শ্রুতিমধুর হওয়া জরুরি, এ সব বিবেচনা তাদের মাঝে একেবারেই কাজ করে না।
যাদের মাথায় খেলে, তারা আবার অন্যভাবে নাম নিয়ে জট পাকান। কেউ হয়তো বা তার সন্তানের নামকরণের জন্য কোনো এক হুজুরের কাছে গেলেন - হুজুর কিতাব-কোরআন দেখে একটি সহি নাম রেখে দিলেন - মনে করুন, ‘সানাহ্উল্লাহ্’। ভদ্রলোক ‘সানাহ্’-র মানে না বুঝে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় নামটি বদলে ফেললেন - ‘সোনাউল্লাহ্’ - যার কোনো অর্থই হয় না। ইমাম সাহেব হয়ত আরও কারো নাম রেখে দিলেন, ‘আব্দুস সোবহান’ - মা-বাপ সংক্ষেপ করার জন্য প্রথম অংশ বাদ দিয়ে রাখলেন - ‘সোবহান’। তারপর এটাও আবার আরও সরল ও বিকৃত হতে হতে হয়ে গেল ‘সোবান’ - ‘সুফান’ - কিংবা ‘তুফান’। এভাবে অঘটন যখন ঘটতে শুরু করে তখন বোঝা যায় না। যখন সমস্যা ও তার জটিলতা স্পষ্ট হয়ে সবার চোখে ধরা দেয়, তখন বড্ড দেরি হয়ে যায়, তেমন কিছু আর করার থাকে না। প্রতিদিন নামের বিষাক্ত বিষ পান করে করে আচানক নামধারীদের বাকি জীবন পার করতে হয়! যিনি অনুভব করেন তার জন্য এ যন্ত্রণা, যার এ বোধশক্তিই নেই তার জন্য শুধু ‘তাইরে নাইরে না!’
নামের ব্যাপারে কোনো কোনো সময় আরেকটি বিবেচনা বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। আমাদের গ্রামের পাশের গ্রামে এক অন্ধ বৃদ্ধা মহিলা থাকতেন। তিনি ভিক্ষে করতেন তার ছেলের হাত ধরে ধরে। ছেলের নাম ছিল ‘রহমত’ এবং গোটা অঞ্চলে ওই ভিখারিণী ‘রহমত-এর মা’ নামেই পরিচিত ছিলেন। ‘রহমত’-এর নানা-নানী তার মায়ের জন্য আদৌ কোনো নাম রেখেছিলেন কিনা সেটা ‘রহমত’- জানতেন কি না সে কথা অজানা, কিন্তু এলাকার অন্য কেউও জানতেন না। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে হামেশা ‘রহমত’ ও তার মায়ের সাথে আমাদের দেখা হত। ওই সময় যদি দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গ সম্মন্ধে আমার আজকের মত দৃষ্টিভঙ্গি ও স্পর্শকাতরতা থাকত তাহলে অবশ্যই আমি একদিন না একদিন ‘রহমত’-এর মায়ের কাছে জানতে চাইতাম, তার নাম কী। বেশ কয়েক বছর আগে এই কিসিমের আরেকটি নাম শুনেছি ঢাকার এক টিভি টক শোতে। নামহীন মানুষের উদাহরণ দিতে গিয়ে এক বড় সরকারি কর্মকর্তা বলেছিলেন, ভোটার লিস্টে এক ভদ্রমহিলার নাম উঠেছে, ‘অ্যারোপ্লেনের মা’।
এখানে ‘রহমত’-এর মায়ের মত ‘অ্যারোপ্লেনের মা’কে নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই, তবে আমি একটি গোলকধাঁধায় পড়েছি ‘অ্যারোপ্লেন’-কে নিয়ে। আমার প্রশ্ন, ‘অ্যারোপ্লেন’ ছেলে না মেয়ে? অবশ্য আজকাল অনেক উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে ছেলেমেয়েদের এমন সব নাম নাম রাখা হয় যে, স্রেফ নাম থেকে বোঝা যায় না, ব্যক্তিটি নারী না পুরুষ - যেমন শামীম, শাহীন, নাসিম, শাওন, রাঙা, কাজল, মাখন, ইত্যাদি।
এ নিয়ে একটি মজার গল্প আছে - আসলে গল্প নয়, এটি একটি সত্য ঘটনা। এই সত্য ঘটনার বয়ান আমার ভাষায় শুনতে চাইলে এ রকম শোনাবে: এই জাতীয় নামধারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তুখোড় ছাত্রী একবার লাইব্রেরির ফ্রন্ট ডেস্কে গিয়ে কর্মরত ক্লার্কের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, ‘আমার বইটা নিতে এসেছি’। কর্মচারি ওই সময় মাথা টেবিলের দিকে নিচু করে কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মাথা না তুলেই তিনি বললেন, নাম কী? মেয়েটি বলল, ‘শামীম চোধুরী’। দায়িত্বরত কর্মচারির নতুন প্রশ্ন, ‘ছেলে না মেয়ে?’ ‘কণ্ঠ শুনে কি মনে হয়?’ মেয়েটির বুদ্ধিদীপ্ত তির্যক উত্তর। ‘বুঝতে তো পারছি না’, বললেন লাইব্রেরির কর্মচারি। ‘মুখ তুলে চেয়ে দেখুন’, শেষ সওয়ালের শেষ জওয়াব দিল শামীম। (মেয়েটির আসল নাম এই তালিকাতেই আছে, তবে আমি ইচ্ছে করে অন্য একটি নাম ব্যবহার করেছি।)
শামীমের ‘মুখ তুলে চাওয়ার’ কথাটি নিতান্তই রুক্ষ ও শুষ্ক, এখানে আবেগ অনুভূতি কিংবা মায়া-মমতার লেশ মাত্র নেই, অথচ এরকমই আরেকটি কথোপকথন আমি শুনেছি, যা কিনা হৃদয়ের গভীর আবেগ ও উচ্ছাস নিয়ে উৎসারিত! শুনবেন সে কাহিনি? এটিও কল্পকাহিনি নয়, বাস্তবে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা মাত্র। কয়েক বছর আগের কথা। একদিন কলকাতার ‘তারা’ টিভিতে জনপ্রিয় সঙ্গীতানুষ্ঠান ‘আজ সকালের আমন্ত্রণে’ দেখছি। ওই দিন ওই অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা ছিলেন মল্লিকা মজুমদার ( প্রখ্যাত সাহিত্যসমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের নাতনী) এবং যন্ত্রশিল্পী হিসেবে কিবোর্ডে ছিলেন ‘রানা’ ও তবলায় ‘প্রসেঞ্জিৎ’। এদের মাঝে ‘রানা’ অত্যন্ত বিনয়ী এবং লাজুক প্রকৃতির লোক। সেদিনকার নিমন্ত্রণে সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে কে এসেছিলেন সে কথা আজ আমার মনে নেই। অনুষ্ঠানের শুরুতে অথবা মাঝখানে কোনো এক সময় রানা-দার প্রশংসা হচ্ছে - তিনি নিজের এত তারিফ শুনে লজ্জায় গুটিসুটি মেরে মুখ নিচু করে হাত কচলাচ্ছেন। রানা দা’র এই লাজুক লাজুক ভাব দেখে, মল্লিকা তার হৃদয়ের সমস্থ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা নিংড়িয়ে বলে উঠলেন, ‘রানা দা’, এত শরম কিসের, মুখ তুলে চাও না একবার!’ অকৃত্রিম মমতামাখা ছোট্ট ওই বাক্যটি মল্লিকার বিগলিত কণ্ঠে এমনভাবে উচ্চারিত হলো যে, আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল! বোঝা গেল, তাদের মাঝে রক্তের সম্পর্ক নেই, আত্মীয়তার বন্ধন নেই, অথচ তারা এক জন আরেক জনকে কত আপন, কত কাছের মানুষ মনে করেন! তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের এই অভাবনীয় অভিব্যক্তিতে আমি অভিভূত ও বিস্মিত না হয়ে পারিনি!
গ্রাম বাংলায় ‘ঝাড়’–, ‘তাড়–’, ‘খড়ম’, ‘ভূত’, ‘পেত্মী’ এ জাতীয় উদ্ভট নামকরণের পেছনেও একটি মারাত্মক কুসংস্কার কাজ করে থাকে। কোনো মা-বাবা যদি কোনো অজ্ঞাত কারণে শিশু বয়সে অথবা কোনো নির্দিষ্ট বয়সে পর পর তাদের সন্তান হারাতে থাকেন, তাহলে এই কুসংস্কার ধন্বন্তরির মত কাজ করে, তবে এই ‘ধন্বন্তরি’, রোগ সারায় না, বরং এটাই রোগের সকল আধার। ভুক্তভুগি মা-বাবারা তখন মনে করেন, সন্তানের নাম যদি অর্থহীন ও অতি অপমানজনক কিছু রাখা হয় তাহলে যমের নজর পড়বে না, শিশুটি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাবে। এ সব নিতান্তই অন্ধকারাচ্ছন্ন কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়।
আজ মনে পড়ে, ‘রহমত’-এর গ্রামে আরো দু’জন মানুষ ছিলেন, এক জন ছিলেন বোবা, তার নাম কী ছিল জানি না, সবাই তাকে ‘আবরা’ বলে ডাকতেন। তার মা এক সময় নিয়মিত আমাদের বাড়িতে কাজ করতেন। তাকে সবাই ডাকতেন ‘আবরা’-র মা। এখন আফসোস হয়, কেন ‘আবরা’-র মাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম না, তিনি ‘আবরা’-কে কী নামে ডাকেন, আর তার নিজের নামই বা কী। একই গ্রামে বয়স্ক আরেক জন মানুষ ছিলেন, তার নাম ছিল ‘খদই’। ‘খদই’ কানে খাটো ছিলেন, তাই তাকে ডাকা হত, ‘খদই কালুয়া’। এভাবে গ্রামের লোকজন খোঁড়াকে ‘লেংড়া’ এবং অন্ধকে ‘কানা’ বলে হরদম ডেকে যাচ্ছেন। কেউ এর প্রতিবাদও করছেন না, কেউ কাউকে এ ভুলও ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছেন না। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে অব্যাহতভাবে সবাই এই গর্হিত কাজটি করে যাচ্ছেন। আমার ধারণা, একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে, নাম নিয়ে এ সব কুকাম ও কুসংস্কারের অবসান ঘটেছে।
নামের সঙ্গে সামাজিক মর্যাদারও একটি যোগসূত্র আছে বৈকি। ধরুন, একজন মানুষ সমাজের নিচুতলার ‘কিরান’ অথবা ‘মাইমাল’ সস্প্রদায়ে জন্মেছেন। ‘শ্রী গোবিন্দ’-এর মত তার বাবা তার নাম রেখেছেন, ‘মুণ্ডু মিঞা’। ‘মুণ্ডু মিঞা’ লেখা পড়া শিখে আপন যোগ্যতায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এখন তিনি তার বাপ-দাদার দেওয়া অর্থহীন বিদঘুটে নাম বদলিয়ে একটি রুচিশীল সুন্দর নাম রাখতে চান। মনে করুন, ‘মুণ্ডু মিঞা’ এখন ‘মাহমুদ হাসান’-এ রূপান্তরিত হলেন। এ বিষয়টিকে সমাজ ও সভ্যতা কীভাবে নেয়? আমার অভিজ্ঞতা, ভালোভাবে নেয় না। ‘মুণ্ডু মিঞা’-র প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনরা এ নিয়ে তার সাথে ঠাট্টা-মসকরা, বিদ্রুপ ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যসহ তার মুণ্ডুপাত করে গাঁ ভাসিয়ে দেবে। বলাবলি করবে - ‘‘মুণ্ডু’-র কাণ্ড দেখেছ, সে এখন ‘মুই কী হনুরে!’ তার সাহস কত, বাপ-মার দেওয়া নাম সে বদলে ফেলেছে!’ ঠোঁট কাটা কেউ থাকলে মুখের ওপর বলে দেবে, ‘তুই অমুকের ছেলে, অমুকের নাতী, তোর নাম তো এ রকমই হওয়ার কথা। তুই কি নাম বদলিয়ে জাতে উঠতে চাস’? ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে সিলেটি দেবনাগরী হরফে লেখা ‘কড়িনামা’ পুঁথিতে আছে:
‘...আগে লাগে উল্লা-টুল্লা পাছে লাগে উদ্দিন
আগের মাম্মদ পাছে যায় কপাল বাড়ে যেদিন’।
বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে প্রচলিত নামকরণের বিভিন্ন তরিকা ও উদাহরণ দেওয়া যায় মোটামুটি এভাবে: ১. সম্পূর্ণ আরবি - আব্দুর রহমান, নাজমুন্নাহার; ২. সম্পূর্ণ ফার্সী - জাবেদ জাহাঙ্গীর, শবনম মুস্তারী; ৩. আরবি-ফার্সী মিশ্রিত - শামীম হাসান, আসমা গুলনাহার; ৪. সম্পূর্ণ বাংলা - স্বপ্নীল সজীব; তারা কুসুম; ৫. আরবি-বাংলা মিশ্রিত - কবির বকুল, শান্তা ইসলাম; ৬. ফার্সী-বাংলা মিশ্রিত - তনয় আফসার, আলেয়া সুন্দরী; ৭. ইংরেজি-বাংলা - সৌরভ মিল্টন, নন্দিতা জেসমিন; ৮. ইংরেজি-আরবি - জুয়েল হাবিব, বিউটি সুলতানা। ৯. অর্থহীন নাম - রৈয়া, তৈয়া, মনফই; ১০. অপমানসূচক - ঝাড়–, ঝাটা, খড়ম, ইত্যাদি।
দেশ-কাল এবং অঞ্চল ভেদেও নামের তারতম্য হয়। একই নাম একেক জায়গায় একেকভাবে রাখা হয়। যেমন বাংলাদেশে আমরা নাম রাখি ‘খালেদ’। এই নাম পাকিস্তান কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে গেলে হয়ে যাবে - ‘খালিদ’। ইংরেজিতে প্রধানত আমরা এভাবে - ‘Chowdhury’ লিখি, কিন্তু সীমান্ত পাড়ি দিলেই এটা ভিন্ন রূপ নিয়ে নেয় যেমন - ‘Chaudhary’ or ‘Chaudhury’, or ‘Choudhury’। পাঁচ-ছয় দশক আগে সিলেট অঞ্চলের গ্রামদেশে বেশিরভাগ নামের সাথে ‘আলী’ যুক্ত করা হত। আজকাল আর হয় না। বোধ করি, নামেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে।
আবার একই বাংলাদেশে, একই সময়ে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের নামের আধিক্য দেখা যায়। ছাত্রাবস্থায় বিষয়টি খুবই সুন্দরভাবে একদিন ক্লাসে তুলে ধরেছিলেন আমাদের প্রিয় শিক্ষক, বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক প্রয়াত আব্দুল মান্নান সৈয়দ। তখন আমি এমসি ইন্টারমেডিয়েট কলেজে (বর্তমানে সিলেট সরকারি মহাবিদ্যালয়) পড়ি। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ক্লাসের প্রারম্ভে একদিন রোলকলের সময় স্যার নাম ডাকতে ডাকতে কী মনে করে হঠাৎ নাটকীয়ভাবে থেমে গেলেন। পুরো ক্লাসের দিকে মুখ তুলে বললেন, ‘সিলেটিদের নাম পড়তে গেলে আমি ঘন ঘন হোঁচট খাই, কোনটা মূল নাম আর কোনটা তার অলঙ্কার, বুঝতে পারি না’। এ কথা বলে স্যার যে সব নামের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন সেগুলো হলো - আলী আহমদ, আহমদ আলী, রহমান আলী, ইসলাম উদ্দিন, ইত্যাদি। ক্লাসে রোলকলের সময় ওই সব নাম আসলে তিনি নীরবে একা একা উপভোগ করতেন, মুচকি মুচকি হাসতেন, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বিদ্রুপ বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন না।
অবশ্য আমি এখন অন্য একটি বিষয় আপনাদের নজরে আনতে চাই। সিলেট অঞ্চলে কয়েকটি ব্যতিক্রমধর্মী নাম রাখা হয় যেটা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাই নেই বললেই চলে। এগুলো হলো আছদ্দর আলী, মছদ্দর আলী, গুরফান আলী, ফরমুজ আলী, মোশাইদ আলী, নিমার আলী, তজম্মুল আলী, কিতাব আলী, ইজ্জাদ আলী, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমি যখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন আমাদের দু’তিন বছর পর সিলেট থেকে এক ছেলে এসে গণিত বিভাগে ভর্তি হলো, তার নাম ছিল ‘কিতাব আলী’। ‘কিতাব আলী’ ছাত্র হিসেবে কেমন ছিল জানি না, তবে সে একজন সুঠাম দেহের অধিকারী ও চৌকস ক্রিড়াবিদ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিন হাজারো দর্শকের সামনে, সে লং জাম্প অথবা হাই জাম্পের জন্য কসরত করে চূড়ান্ত অ্যাকশনের দিকে রাজার মতন হেলে দুলে দৌড়ে আসছে - ওই মুহূর্তে দু’পাশ থেকে দর্শকছাত্ররা সমস্বরে চিৎকার করে বলে উঠত - ‘পুস্তক আলী’, ‘বুক আলী’, ‘বই আলী’ ইত্যাদি, ইত্যাদি। যদিও আমি কোনো দিন এ জাতীয় বিদ্রুপানন্দে শরিক হইনি, তথাপি তখন আমি জানতাম না যে, কারো নাম বিকৃত করা একটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ!
নামকরণ নিয়ে আমি এবার আরেকটু গভীর ও গুরুতর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ষাটের দশকের আমাদের বাড়ির কথা দিয়েই শুরু করি। কিছু ঘটনা ঘটেছে আমার জন্মের আগে, বাকিগুলো যখন ঘটে তখন আমার বয়স আঠারো-কুড়ি, বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু চিন্তায় পরিচ্ছন্নতা ও পরিপক্কতা আসেনি, আসলেও কাজ হত না, কারণ ওই বয়সে বাড়ির কোনো সিদ্ধান্তকে কোনোভাবে প্রভাবিত করার মত অবস্থান আমার ছিল না, থাকার কথাও নয়। আমাদের বাড়ি ছিল একটি বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের আবাসস্থল। তার আয়-উপার্জন ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। আব্বা ছিলেন সবার বড় এবং বাড়ির মুরব্বী। তিনি স্থানীয় হাই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, ষাটের দশকে মাইনে পেতেন দেড়’শ’ কি দু’শ’ টাকা। বড়চাচা ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তার মাসিক সম্মানী ছিল মাত্র পঞ্চাশ টাকা। চাচার পদ-পদবীর সুবাদে মানুষের আনাগোনায় আমাদের বাড়ি সব সময় রম রম গম গম করত। বাড়িতে নারী-পুরুষ ছোট-বড় মিলে কাজের লোক ছিল কমসে কম দশ-বারো জন। নারী কর্মীদের নগদ পারিশ্রমিকের কোনো কারবারই ছিল না, তবে কাজের বিনিময়ে দু’বেলা পেট ভরে খাওয়া এবং যাওয়ার সময় ছেলেমেয়েদের জন্য পোঁটলা বেঁধে নিয়ে যাওয়াটা ব্যতিক্রমের চেয়ে নিয়মেই পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বেটামানুষদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল বেতনভুক; বংশানুক্রমিকভাবে কয়েক জন পেটেভাতেও ছিলেন। বেতনছাড়াদের মর্যাদা বেতনওয়ালাদের উপরে ছিল, কারণ তাদেরকে অনেকটা পরিবারের সদস্য হিসেবেই গণ্য করা হত। এই তফাৎটা তারাও বুঝতেন এবং এর সুবিধাও নিতেন ষোল আনা। কিভাবে সে কথা এখানে আর নাই বা বললাম। এমনি মর্যাদাবান একজনের নাম ছিল ‘চটর’। বয়স বিবেচনায় তাকে আমরা ‘চটর’-চাচা বলে ডাকতাম।
আমার জন্মের অনেক আগে শিশু ‘চটর’ চাচা তার মা-বাবার সাথে আমাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নেন। আমার ধারণা, তারা সিলেট অঞ্চলের কোনো চা বাগানের কুলি ছিলেন, কোনো কারণে হয়তো বাগান কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বের করে দেন অথবা তারা পালিয়ে আসেন। এমনও হতে পারে যে, কেবল ‘চটর’ চাচার বাবা-মা-ই এসেছিলেন এবং পরে আমাদের বাড়িতেই তার জন্ম হয়েছিল। ‘চটর’ চাচার মাকে আমি দেখেছি, তার বাবাকে দেখিনি । ‘চটর’ চাচার বাবার নাম ছিল ‘মটর’। যেহেতু তার নাম ‘মটর’, তাই তার স্ত্রীর নাম রাখা হলো - ‘মটরনি’। আর ‘মটর-মটরনি’র ছেলের নাম হয়ে গেল ‘চটর’। ‘মটর’, ‘মটরনি’ ও ‘চটর’ এগুলো সবই অর্থহীন নাম। কে রেখেছিল জানি না, কোনো দিন কাউকে জিজ্ঞেসও করিনি, সময়কালে আব্বাকে প্রশ্ন করলে হয়তো এ রহস্যের সুরাহা হত। এই জাতীয় নামকরণের মাধ্যমে কাজের মানুষের প্রতি আমার পূর্বপুরুষদের একটি দারুণ অবহেলা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিলের ভাব স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে! এমন নামকরণ যদি আমার বাপ-দাদারা নাও করে থাকেন, তথাপি শোনার পর তাদের উচিৎ ছিল নামগুলো বদলে দেওয়া, নিজে করতে না পারলে, বাড়িতে মসজিদের ইমাম থাকতেন, বললেই তিনি তাদের জন্য সুন্দর সুন্দর তিনটি নাম রেখে দিতে পারতেন।
একই রকমের অন্য এক কাজের লোকের বেলা এ জাতীয় একটি ঘটনা ঘটেছেও, তবে অনেক পরে। আম্মার বিয়ের সময় তার ফুট-ফরমায়েস খাটার জন্য নানা একটি ছোট্ট ছেলেকে আম্মার সঙ্গে দিয়েছিলেন। সে ও তার মা, ‘চটর’ আর ‘মটরনি’র মতন আমার নানার বাড়িতে আশ্রিত ছিল। ছেলেটির নাম ছিল ‘উদভ’ তার মায়ের নাম ‘কাঞ্চন’। ‘উদভ’ যখন আমাদের বাড়িতে আসে তখন তার বয়স ছিল বড়জোর তিন কি চার। সে শুধুই আমাদের কোলেকাঁখে মানুষ করেনি, সময় সময় আমাদের খেলার সাথীও ছিল। টুকটাক কাজও করত আবার আমাদের সঙ্গও দিত। ‘উদভ’ যখন বিশ/একুশ তখন আমাদের মসজিদের ইমাম তার নাম বদলে দিয়ে রাখলেন ‘জমির আলী’। তার পর থেকে সে ‘জমির আলী’ই হয়ে গেল। আমরা তাকে তার নামদস্তখত শিখিয়ে দিলাম।
এ দিকে কালের আবর্তে ‘চটর’ চাচা বিয়ে করলেন। দু’এক বছর পর যখন তার এক মেয়ে হলো, তিনি সখ করে শিশু ‘চটর’-এর নাম রাখলেন, ‘খাজুরি’। তারপর যখন তার আরেক মেয়ে হলো, তখন তিনি নাম রাখলেন ‘এলাছুন’, কিন্তু বাড়ির কেউই এই নাম গ্রহণ করলেন না। তাদের ভাবখানা, ‘খাজুরি’-র বোন ‘তেজুরি’, এটাই তো যথেষ্ট, ‘এলাছুন’-এর আবার দরকার কী। এভাবে সবাই তাকে ‘তেজুরি’ ডাকতে শুরু করে দিলেন। এতে করে মেয়েটির আপন বাবার দেওয়া নাম ‘এলাছুন’ হাওয়ায় হারিয়ে গেল। ‘এলাছুন’ হয়ে গেল, ‘তেজুরি’। ‘চটর’ চাচা নিরুপায়, তার কিছু বলারও নেই, করারও নেই। তিনি যে বাড়িতে পেটেভাতে কাজের লোক! এগুলো সব আমার চোখের সামনে হচ্ছে, এখানে যে একটি অবহেলা তুচ্ছ-তাচ্ছিলের খেলা চলছে সে সব বিষয় তখন বিলকুল আমার মাথায় আসেনি। গল্পের এখানেই শেষ নয়, আরও আছে।
জমিরের বয়স যখন ২৪/২৫ তখন আমি কলেজে পড়ি। ওই সময় ‘জমির’-এর সঙ্গে ‘খাজুরি’র বিয়ে হলো। দু’এক বছরের মধ্যেই তাদের ঘরে ফুটফুটে এক ছেলের জন্ম হলো। মা-বাবাকে আপন ছেলের নাম রাখার সুযোগ না দিয়ে আমার ছোট ভাইয়েরা ভাবলো, ‘জমির’-এর ছেলে, তাই তার নাম হওয়া উচিৎ ‘ছমির’। ব্যাস ‘জমির’-এর ছেলের নাম হয়ে গেল ‘ছমির’। তার পর মাস যায়, বছর যায়, আমি কানাডায়, আমার ভাইবোনেরা কলেজে পড়তে এদিক-ওদিক চলে গেল, আব্বা মারা গেলেন। আম্মাও বাড়ি ছেড়ে প্রথমে সিলেট পরে ঢাকায় থাকতেন। পাহারাদার হিসেবে ‘জমির’ই তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়ির ‘জমিদার’ হয়ে রইল। জমির আর কাজের লোক নয়, সে এখন বাড়ির ‘রাজা’। ঊনিশ শ’ সাতানব্বইতে বাড়ি গেলাম। গিয়ে দেখি, জমিরের ছেলে ‘ছমির’ লায়েক হয়েছে, সে দুবাই যাবে, ‘চটর’ চাচা তার শেষ সম্বলটুকু (এক টুকরা জমি) বিক্রি করে টাকা দিয়েছেন। নানার টাকায় নাতী দুবাই যাবে, আহ্লাদে আটকানা! ‘জমির’-এর কুঁড়েঘরে খুশির বন্যা বইছে! এক দিকে ‘ছমির’-এর পাসপোর্ট হয়েছে, আকামাও লেগে গেছে, অন্য দিকে ততদিনে তার নাম বদলে গেছে! ‘ছমির আলী’ এখন আর ‘ছমির আলী’ নেই, সে একজন পেটেভাতে কামলার ছেলেও নয়, বরং সে এখন ‘রাজার’ ছেলে - ‘রাজপুত্র!’ তার উত্তরণ হয়েছে ‘ছমির আলী’ থেকে ‘আমীর আলী’-তে। (আমীর মানে নেতা, বাদশা)। পরিশেষে, আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, নামে যদি কিছু নাই বা আসে যায়, তবে ‘জমির’ কেন তার ছেলের নাম ‘ছমির’ পাল্টে ‘আমীর’ রাখল?
লেখক: আবু এন. এম. ওয়াহিদ; অধ্যাপক - টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটি
এডিটর - জার্নাল অফ ডেভোলাপিং এরিয়াজ
Email: awahid2569@gmail.com
** লেখার মতামত লেখকের। একুশে টেলিভিশনের সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে।