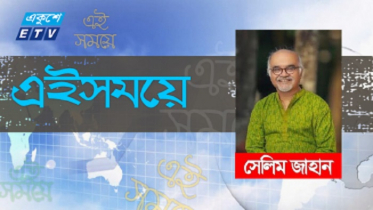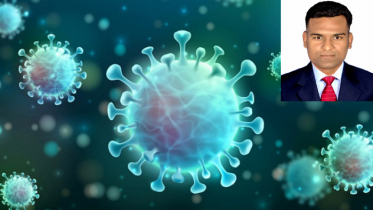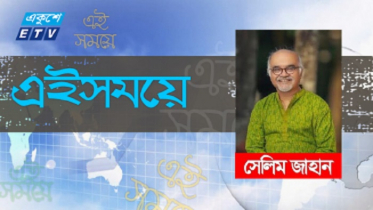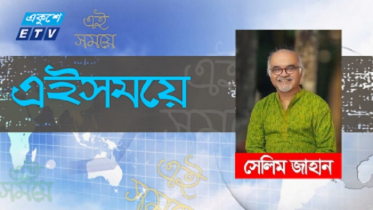মঙ্গল শোভাযাত্রা অভিনব ও চিরায়ত
প্রকাশিত : ১০:১২, ১৪ এপ্রিল ২০১৮

মঙ্গল শোভাযাত্রা একেবারে হালের উৎসব। সমষ্টির কল্যাণ কামনা করে সাজসজ্জা নিয়ে ঢোলনহবৎ বাজিয়ে সম্মিলিতভাবে রাজপথ পরিক্রমণের মধ্যে অভিনবত্ব রয়েছে, তবে এর অবলম্বন যে নতুন বছরের প্রথম দিন, সেখানে রয়েছে চিরায়ত এক মাত্রা। এ চিরায়তের আধার বাঙালির নববর্ষ, বৈশাখের প্রথম দিবস। নববর্ষ আবাহনের পদ্ধতি ইতিহাসের পথপরিক্রমণে নানাভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে বঙ্গভূমিতে সাল-গণনার বিভিন্ন ধরন বজায় ছিল, তার মধ্যে একটা সমন্বয় আনার চেষ্টা করেন মধ্যযুগের মোগল সম্রাট আকবর; তার শাসনামলেই রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্য নিয়ে প্রবর্তিত হয় বঙ্গাব্দ, ফসলি সাল হিসেবে পরিচয়প্রাপ্ত এ বর্ষপঞ্জির সূচনার মাস হিসেবে বৈশাখকে নির্ধারণ করা হয়। সেই সঙ্গে বর্ষগণনার সূচনাকাল হিসেবে ধার্য হয় মক্কা থেকে মদিনায় নবী করিমের (সা.) হিজরত গ্রহণের বছর। ইতিহাসই বুঝি বাঙালির ললাটে মিলন-মিশ্রণের সংস্কৃতির তিলক কেটে দিয়েছিল এবং অন্তঃসলিলাভাবে হলেও সেই পরিচয় বহন করছে বাংলা বর্ষপঞ্জি। হিন্দু পণ্ডিতের সব আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব যে পঞ্জিকা অনুসারে নির্ধারিত হচ্ছে, সেখানে ইসলামের ইতিহাসের সম্পৃক্তি তাই রয়ে গেছে অমোচনীয়ভাবে।
ফসলি সালের সঙ্গে বাংলা বর্ষবরণের যে যোগ সেটা ঔপনিবেশিক আমলে ক্ষীণভাবে বহমান ছিল জমিদারের খাজনা আদায় ও পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে, আর এর জের হিসেবে টিকেছিল ব্যবসায়ীদের হালখাতা অনুষ্ঠান, যখন সাবেকি ধারকর্জ চুকিয়ে নতুনভাবে খোলা হতো হিসাবের খাতা। সমাজজীবনে এই উৎসব আনন্দময় ও কর্ম-প্রাসঙ্গিক করে তোলার অবলম্বন ছিল বৈশাখী মেলা। এসব মিলেই গড়ে উঠেছিল বাঙালির বর্ষ-আবাহনের চারিত্র্য, এর সঙ্গে ধর্মের যোগ ছিল, তবে তা ছিল অপ্রধান। চৈত্রসংক্রান্তি কিংবা শিবের গাজনে এর যে প্রকাশ সেখানে ধর্মাচারের পাশাপাশি ছিল লোকাচার; লোকরঞ্জক ভূমিকা ছিল প্রধান। সেই বিচারে বৈশাখ ঘিরে বাঙালি সমাজে আলোড়নের ছিল এক সেকুলার মাত্রা এবং ছিল সর্বজনীনতা।
দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন পদানত জাতিগুলোর ঐতিহ্যিক জীবনধারা তছনছ করে দিয়েছিল। আফ্রিকার বহু দেশে তা পাল্টে দিয়েছিল জনগোষ্ঠীর ধর্ম, তাদের ভাষা, আচার, পোশাক; কিন্তু সবকিছুর পরও একেবারে মুছে দেওয়া যায়নি তাদের লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি। নাগরিক সংস্কৃতি নিজ দেশ ও নিজ সমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করলেও অন্তরের গভীরে নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য জাতি নানাভাবে লালন করে চলেছিল। জাতির পুনর্জাগরণ ও সংহতি রচনায় তাই সংস্কৃতি পালন করেছিল নিয়ামক ভূমিকা। আফ্রিকার বহু দেশের মানুষ ভুলে গেছে তাদের মাতৃভাষা, হারিয়েছে তাদের ধর্ম, তাদের নাম-পদবি। শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যসন-ভূষণ, জীবনবৃত্তি ও জীবনাচারে তারা শেকড়চ্যুত রয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম, সেই পতিত জনগোষ্ঠীর জন্যও তো জাগরণের অবলম্বন হয়েছিল সংস্কৃতি। পতিত দশার উদাহরণ হিসেবে মনে পড়ে সেনেগালের কবি ও রাষ্ট্রপতি লিওপোল্ড সেংঘর সম্পর্কে পাশ্চাত্যের উচ্ছ্বাসের বিপরীতে এক আফ্রিকি তরুণ বীতশ্রদ্ধভাবে আমাকে বলেছিল, সেংঘর ফরাসিতে কথা বলেন, ফরাসিতে কবিতা লেখেন এবং এমনকি ফরাসিতে স্বপ্ন দেখেন। এর পাশাপাশি জাগরণের সূত্র হিসেবে আমরা দাখিল করতে পারি আফ্রিকার মুক্তি-আন্দোলনের নেতা গিনি-বিসাউয়ের আমিলকার কাবরালের উক্তি, সত্তরের দশকে ইউনেস্কোর এক সেমিনারে তিনি বলেছিলেন, অ্যান অ্যাক্ট অব কালচার ইজ অ্যান অ্যাক্ট অব লিবারেশন, সাংস্কৃতিক কোনো কর্মকাণ্ড নিহিতার্থে মুক্তিরই কর্মপ্রয়াস। নিজের দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বুঝেছিলেন, আফ্রিকানরা যখন হারিয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, পদানত জাতি হিসেবে খুইয়েছে তার অর্থনৈতিক-সামাজিক অধিকার ও স্বকীয়তা, নগরে প্রশ্রয় পেয়েছে ভিনদেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি, তখনও রয়ে যায় তার লোকায়ত সংস্কৃতি, হয়তো প্রকাশ্য নয়, সরব নয়, মূলধারায় তার অবস্থান নেই; কিন্তু দূর অরণ্যে পাহাড়ের কন্দরে কেউ যখন মাদলে বাজায় বোল, মেতে ওঠে গানে-নৃত্যে, সেখানেই মেলে জাতি ও জনগোষ্ঠীর নিজেকে আবার ফিরে পাওয়ার অবলম্বন, জাগরণের সূত্র।
তবে এসব তো তত্ত্বের কথা। বাস্তবের দিকে মুখ ফেরালে আমরা দেখি সাতচল্লিশের দেশভাগ সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের ভিত্তিতে যে বিভাজন ও বিদ্বেষ সমাজে আরোপ করেছিল, দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক যে ধর্মীয় জাতীয়তাবোধ চাপিয়ে মুছে ফেলতে চেয়েছিল বাঙালি সত্তা, তার বিপরীতে বাঙালির জাগরণ ছিল ভাষাভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক জাতিচেতনা নিয়ে, স্বভাবগতভাবে যা অসাম্প্রদায়িক, বিভাজনের বিপরীতে সংযুক্তির আদর্শবহ। এরই অসাধারণ প্রকাশ আমরা পাই বাংলা ভাষার অধিকারের দাবিতে একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলনে, যা বাঙালিকে সচকিত করেছিল নিজ সংস্কৃতি বিষয়ে এবং জুগিয়েছিল এ উপলব্ধি যে, ধর্ম-পরিচয় জাতিসত্তা মুছে ফেলে না, বরং নানা ধর্মের মানুষের মিলনক্ষেত্র রচনা করে জাতীয়তা, বাংলার হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-মুসলমান সবাই বাঙালি পরিচয়ে ভূষিত ও গর্বিত। কিন্তু বাঙালিত্ব দমন করে মুসলিম ধর্ম-পরিচয়কে জাতি-পরিচয় হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার জবরদস্তিতায় মেতে উঠেছিল পাকিস্তান। অথচ পাকিস্তান তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্র হলেও সে দেশে পাঠান-পাঞ্জাবি-বেলুচ-সিন্ধিদের অবস্থান ও জাতি-পরিচয় মুছে দেয়ার সাধ্য তার নিজেরও হয়নি। বাঙালিত্ব খারিজ করতে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে শাসকগোষ্ঠী এক সময় কায়েম করেছিল এক ইউনিট, বাতিল করেছিল সেখানকার জাতিভিত্তিক প্রদেশগুলো, যেন পাকিস্তানে কোনো জাতিসত্তা নেই, আছে কেবল ইউনিট। সেই এক ইউনিটও বাতিল হল বাঙালির আন্দোলনের ফলে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনকালে। পাকিস্তান আবার ফিরে পেল জাতিসত্তাভিত্তিক প্রদেশগুলো, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের পক্ষেও জাতিসত্তা অস্বীকার করা যে সম্ভব নয়, এ ছিল তার আরেক প্রকাশ।
একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল ভাষার সূত্রে, হয়েছিল সাংস্কৃতিক জাগরণের অবলম্বন, শেকড়ের সন্ধানে যাত্রা, মিলনক্ষেত্র তৈরির পরিসর। ভাষাকে অবলম্বন করে শুরু হয়েছিল পূর্ব বাংলার বাঙালির ব্যতিক্রমী জাগরণ, শহীদ মিনার হয়ে উঠল যার প্রতীক, যে প্রতীক ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে, সেকুলার এক সম্মিলনী রূপে।
বাঙালির মিলনের এ উপলক্ষ চরিত্রগতভাবে সাংস্কৃতিক এবং কাঠামোগতভাবে রাজনৈতিক। একুশে জাতির অন্তরে মূর্ত হয়ে ওঠার পেছনে সাহিত্যিক-সাঙ্গীতিক-সাংস্কৃতিক উদ্যোগগুলোই ছিল প্রধান। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত আলতাফ মাহমুদ সুরারোপিত প্রভাতসঙ্গীত ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, তবে একমাত্র নয়। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ সংকলন সাহিত্যিক যৌথতার নবযাত্রা সূচিত করেছিল। আরও কতভাবেই না গানে-কবিতায়-গল্পে-উপন্যাসে-চলচ্চিত্রে-নাটকে মূর্ত হয়ে উঠল একুশে এবং জাতির অন্তরে খোদিত করে দিল এর স্থায়ী রূপ, যা প্রতীকী ব্যঞ্জনা পেয়েছিল নভেরা আহমেদ আর হামিদুর রহমান কৃত শহীদ মিনারের নকশায়। ইউনেস্কো যখন একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করল, তখন আমরা উদ্বেলিত হয়েছি বাংলা ভাষার এ বৈশ্বিক স্বীকৃতিতে, তবে আমরা লক্ষ করি না, এর অপর পিঠে রয়েছে বিশ্ব সভ্যতায় বাঙালির অবদান। বিশ্বায়ন আরোপিত সংস্কৃতির সমরূপত্বের সংকটকালে বাঙালির একুশে বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় মাতৃভাষার গুরুত্ব, ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার তাৎপর্য, যা আমরা কোনোভাবে যেন খুইয়ে না ফেলি।
একুশের পথ বেয়ে জাতির সংহত হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন ছিল আরও অনেক কাজ, অনেক উপলক্ষ। তারই জোগান দিল ১৯৬৭ সালে ছায়ানট আয়োজিত রমনার অশ্বত্থ-তলে বর্ষবরণের সঙ্গীতানুষ্ঠান। উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রকৃতির আশ্রয়ে নতুন বছরের প্রথম প্রভাতে ভৈরবী রাগনির্ভর যে সুর ভেসে এলো তা জাতিকে অনুপ্রাণিত করল বিপুলভাবে। এ উৎসব অচিরেই পেল প্রতীকী মর্যাদা এবং ক্রমে পেতে শুরু করল বিস্তার। নগর থেকে বিতাড়িত বাংলা নববর্ষ আবার ফিরে এলো শহরে নতুন মাত্রা নিয়ে। নতুন করে সবার নজর ফিরল গ্রামীণ বর্ষবরণ, গ্রামীণ মেলা ও ক্রীড়া নবপ্রাণ লাভের সুযোগ যেন পেল এবার।
ছায়ানটের এমন সীমিত আকারের ছোট আয়োজন যে এত প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারল তার কারণ এমন এক উৎসবের জন্য জাতি বুঝি প্রস্তুত হয়েছিল। বৈশাখ হয়ে উঠল বাঙালির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উৎসব-আয়োজন। এই বাঙালিই বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে রাজনৈতিক ঐক্য সংহত করেছিল জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে এবং একাত্তরে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতা।
স্বাধীন বাংলাদেশে বৈশাখী উৎসব ক্রমে বিস্তৃতি অর্জন করেছে, শেকড়ের সন্ধানে বাঙালি আরও নিষ্ঠাবান হতে চেয়েছে এবং খুঁজে ফিরছে জাতীয় মানস ও জাতীয় সংস্কৃতির রূপ। বাধা-বিঘ্ন এসেছে অনেক, বিশেষভাবে বাঙালিকে তার অসাম্প্রদায়িক উদার জাতিসত্তা থেকে বিচ্যুত করে ধর্মান্ধতা ও কূপমণ্ডূকতার পথে ঠেলে দিতে আয়োজন হয়ে ওঠে প্রতাপশালী, একপর্যায়ে লাভ করে রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা। সংস্কৃতি ঘিরে চলছিল এক লড়াই। এ প্রয়াসে জাতি যেন দাবি করছিল তার ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত নতুন আরও অনেক আয়োজন, উৎসব-আনন্দে মিলিত হওয়ার আরও অনেক উপলক্ষ।
এ উপলক্ষের জোগান এলো চারুকলা ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে, তরুণ শিক্ষকদের প্রণোদনায়। সমষ্টিমঙ্গল কামনা করে সজ্জিত শোভাযাত্রার ধারণা তাদের মধ্যে দেখা দেয় প্রথম, সেজন্য উপযুক্ত উপলক্ষ খুঁজছিল নবীন শিল্প-শিক্ষার্থীরা, কেবল উপলক্ষ নয়, খুঁজছিল উপযুক্ত ফর্মও, যা প্রকাশ করবে বাঙালির সত্তা ও আকুতি। স্বাভাবিকভাবে অনুমান করা যায়, এ প্রেরণার উৎস শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের শিল্পশিক্ষা, যিনি লোকায়ত শিল্পরূপের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে ছিলেন সদা-উন্মুখ। জয়নুল আবেদিন প্রয়াত হলেও এ শিল্পছাপ রয়ে গিয়েছিল তার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়ে। ১৯৮৬ সালে শিল্প শিক্ষালয়ের নবীন স্নাতকরা যশোরে আয়োজন করেছিল বর্ষবরণের সজ্জিত শোভাযাত্রার। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে জয়নুল জন্মোৎসবে মুখোশ-মুকুট-ফেস্টুন নিয়ে আনন্দ-শোভাযাত্রার আয়োজন করে শিক্ষার্থীরা। এ আয়োজনে লোকসমাজের সাড়া তারা অনুভব করেছিলেন এবং সেটাই তাদের ব্রতী করে বাংলা বর্ষবরণের শোভাযাত্রার আয়োজনে। ১৯৮৯ সালের পহেলা বৈশাখ সকালে ঢাকঢোল নিয়ে সুসজ্জিত যে শোভাযাত্রা বের হয় চারুকলা ইন্সটিটিউট থেকে, তা তারুণ্যের আনন্দ-উৎসব হিসেবে মন কেড়ে নেয় শহরবাসীর। স্বৈরশাসন-পীড়িত বাংলাদেশে বৈশাখের শোভাযাত্রা কেবল আনন্দময় ছিল না, ছিল প্রতিবাদীও। কেবল মনোমুগ্ধকরতা ছিল না এর অবয়বে, ছিল গভীরতাশ্রয়ী অনুসন্ধানও। যেসব প্রতীক তারা বেছে নেন শোভাযাত্রাকারীদের বহন করার জন্য, তার উৎস ছিল লোকশিল্প। ফলে বাংলার বর্ষবরণে অভিনব মাত্রা বয়ে আনল চারুকলা ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে প্রবর্তিত শোভাযাত্রা, পরের বছর যা অভিহিত হল মঙ্গল শোভাযাত্রা হিসেবে এবং চিরায়ত উৎসবের সঙ্গে যুক্ত করে অভিনব মাত্রা।
অশ্বত্থ-তলের বৈশাখী সঙ্গীতায়োজনের মতো, কিংবা তারও চেয়ে অনেক বেশি দ্রুততায়, মঙ্গল শোভাযাত্রা ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। এখানেও চারুকলার স্নাতক কিংবা শিক্ষার্থীদের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। শিল্পশিক্ষা এখন পেয়েছে বিস্তার, ঢাকার বাইরে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে অনেক শিক্ষালয়, তারা হয়েছে মঙ্গল শোভাযাত্রার শৈল্পিক জোগানদার। ঢাকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী কিংবা শিল্প-নবিশরা তাদের নিজ নিজ জেলা-উপজেলা শহরে গিয়ে হাত লাগান মঙ্গল শোভাযাত্রা সজ্জাকরণের কাজে। ফলে বৈশাখের প্রথম প্রভাত প্রায় দেশব্যাপী জাতীয় এক শোভাযাত্রার রূপ নিয়েছে যা অভাবিত, অনন্য ও অভিনব। সাংস্কৃতিক জাগরণে যে শৈল্পিক মাত্রা প্রয়োজন সেটা আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই রাজনীতির চাপে। ছায়ানটের প্রভাতি সঙ্গীতায়োজন কিংবা দেশব্যাপী প্রকৃতির কোলে এমনি সঙ্গীতায়োজনের শৈল্পিক মাত্রাই তাকে এত প্রভাবসঞ্চারী করে তুলতে পেরেছে। এ আয়োজন দেশ, মানুষ, সমাজ, সঙ্গীত, সংস্কৃতি একত্রে গেঁথে প্রকৃতি-বন্দনা ও মানব-বন্দনায় মুখর হয়ে ওঠে। মঙ্গল শোভাযাত্রাও নিছক কোনো আনন্দ-আয়োজন নয়, আনন্দ তার অনুষঙ্গ বটে, তবে সেই সুবাদে এখানে আমরা পাই লোকশিল্পের নবায়ন ও নব-উদ্ভাসন, ঐতিহ্যিক শিল্পের রূপশ্রী অবলম্বন করে সম্মিলিতভাবে রাজপথ পরিক্রমণ নিবিড় এক আনন্দ ও গভীর এক বার্তা সঞ্চার করে সবার মনে। মঙ্গল শোভাযাত্রা সবাইকে একত্র করে শিল্পের ঐতিহ্যিক ধারায়, এর নানা রূপানুসন্ধান শৈল্পিক অভিযাত্রায় ব্রতী করে অনেককে। এ সাধনার সম্মিলিত মাত্রা একে জোগায় জাতীয় জাগরণের নতুন শক্তি। এসবের স্বীকৃতি আমরা দেখি ইউনেস্কোর ঘোষণায়, বাংলাদেশের মঙ্গল শোভাযাত্রা কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটির তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণে। স্বীকৃতি প্রদানের বার্তায় ইউনেস্কো যে উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইউনেস্কো বলেছে, ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা হয়ে উঠেছে সজীব ঐতিহ্য নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের গর্ব, সেই সঙ্গে সত্য ও ন্যায়প্রতিষ্ঠায় এবং অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের প্রত্যয় ও সাহসের পরিচয়।’
মঙ্গল শোভাযাত্রা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে বটে; তবে এর মর্মবাণী সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য আরদ্ধ রয়েছে অনেক কাজ। সমষ্টিমঙ্গলের বার্তা আমরা পাই বৈশাখী শোভাযাত্রা ও প্রভাতি সঙ্গীতের দেশব্যাপী উদ্যোগ আয়োজনে; কিন্তু সমাজে এর প্রতিষ্ঠায় আরও সক্রিয়, আরও প্রত্যয়ী ও আরও সাহসী হওয়ার বাণী আমরা শুনতে পাই সঙ্গীতের ও শোভাযাত্রার আয়োজনে। নতুন বছরে সেই নতুন পণ গ্রহণ করবে বাঙালি- এমনটাই সবার প্রত্যাশা।
মফিদুল হক : সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।
** লেখার মতামত লেখকের। একুশে টেলিভিশনের সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে।