কু...উ...উ
সেলিম জাহান
প্রকাশিত : ০৩:১৪ পিএম, ২৬ জুলাই ২০২০ রবিবার
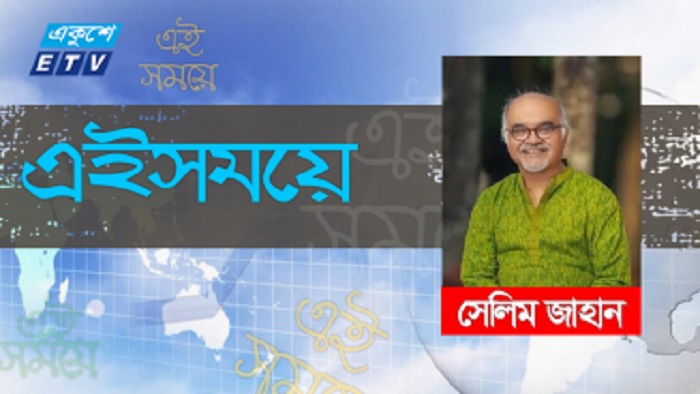
শব্দটি শুনে চমকালাম ভীষণভাবে দু’টি কারণে। প্রথমত: বিদেশে রেলগাড়ী এমন ‘কু ..উ..উ’ শব্দ করে না। বাড়ির পাশ দিয়ে দূরপাল্লার আন্ত:শহর রেলগাড়ী নিত্য সকাল-দুপুর-বিকেল যায়, কিন্তু কখনও তার ‘কু..উ..উ’ শব্দ শুনি নি। আজই শুনলাম। সুতরাং অবাক হওয়ারই কথা। দ্বিতীয়ত: এই ‘কু..উ..উ’ ডাকটি তো আমার শৈশব-কৈশোরের স্মৃতির ডাক, আমার শীতের বেড়ানোর ধ্বনি। সারাটা দিন ধরে সে ডাক আমার হৃদয়ে আর করোটিতে ‘জলের মতো ঘুরে ঘুরে’ কথা কইল।
বাবার কর্মসূত্রের কারণে আমাদের স্হিতু বরিশালে। কিন্তু মাতৃকুল ও পিতৃকুলের বৃহত্তর পরিবারের অবস্হান নোয়াখালীতে। সুতরাং প্রতি শীতে আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ‘দেশে’ যাওয়ার পালা। চাকুরীসূত্রে যে সব আত্মীয়স্বজনেরা বাইরে থাকতেন, তারাও সপরিবারে ‘বাড়িতে’ আসতেন। সুতরাং এ ছিল এক পারিবারিক সম্মিলনী।
আমার মনে আছে, যাওয়ার একমাসে আগেই আমাদের বরিশালের বাড়িতে সে কি গোছগাছ, তোড়জোড়ের ধুম। বাবা স্টীমার, ট্রেনের টিকিটের ব্যবস্হা করছেন, আত্মীয়-স্বজনের জন্য উপহার সামগ্রী কিনছেন, আমাদের অনুপস্হিতিতে কে বাসা পাহারা দেবে তা নিশ্চিত করছেন। আর মার কাজ আমাদের জিনিসপত্র নেয়া, বাড়ি গোছগাছ করা এবং আমাদের পই পই করে আদব কায়দা শেখানো কি করে বড়দের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। শহরের তথাকথিত ‘উল্টোপাল্টা ব্যবহার’ (মা’র ভাষ্য) সেখানে চলবে না। তারপর আমাদের সবাইকে (বাবাসহ) মাতৃকুলের বংশলতিকা মুখস্হ করানো হতো। অজন্তা খালা মা’র চাচাতো বোন, কুসুম খালা মামাতো বোন, তাঁর কানা মামা ছটকু মামার ভাই নন, ছোট নানাকে সালাম করার পর নাম বলতে হবে, কারণ তিনি কানে খাটো।
তারপর শুরু হতো বাঁধাছাঁদার কাজ। শীতকালে ‘হোল্ডঅল’ বলে এক বস্তুতে (এখন বিলুপ্ত) লেপ-তোষক সব বাঁধা হতো। সুটকেস ভরে উঠত কাপড় আর উপহার সামগ্রীতে। টিফিন কেরিয়ারে থরেথরে খাবার সাজানো হতো, কারণ বাইরের খাদ্য মা’র কাছে অস্পৃশ্যসদৃশ। আমাদের অবশ্য পক্ষপাত থাকত বাইরের সব মজাদার খাবারের দিকে। কিন্তু ছোটদের কথা আর কে শোনে?
নির্দিষ্ট দিনে প্রথমে স্টীমারে করে বরিশাল থেকে চাঁদপুর। খুব ভোরে সে স্টীমার পৌঁছাতো চাঁদপুরে। চাঁদপুরে মাছের গন্ধ, লাল ফতুয়া পড়া কুলিদের দাপাদাপি, শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে দৌঁড়-ঝাঁপ করে ট্রেনে ওঠার কথা এখনও মনে আছে। ট্রেনে মালপত্র তোলার পরে চারদিকে কুলিদের সঙ্গে পয়সা নিয়ে বচসা এখনও যেন শুনতে পাই। ট্রেনে উঠেই মা আমাদের সবাইকে গরম কাপড় পরিয়ে দিতেন। তারপর টিফিন কেরিয়ার খুলে আমাদের সবার হাতে সকালের নাস্তা ধরিয়ে দিতেন। এরমধ্যে দেখতাম কোন এক ফাঁকে বাবা মা’র চোখ এড়িয়ে নীচে নেমে ভাঁড়ের ধূমায়িত চা খাচ্ছেন। বড় করুণ নয়নে তাকিয়ে থাকতাম আর ভাবতাম, বড় হলে পরে ঐ ভাড়ওয়ালার সব চা একাই খাবো।
হঠাৎ করে জোরে একটা শব্দ হতো। সবাই বলত, ইঞ্জিন লেগেছে ট্রেনে। একবার ঐ ধাক্কায় বগির মেঝেতে পড়ে গিয়ে মাথায় খুব ব্যথা পেয়েছিলাম, মনে আছে। আস্তে আস্তে ট্রেনটা আড়মোড়া ভাঙ্গতো। চলতেও শুরু করল যেন একটু। দেখতাম গার্ড সাহেব তাঁর সবুজ পতাকা দুলিয়ে দিতেন, বাজত তাঁর বাঁশি। বাবা তখনও নীচে। মা খুব উদ্বিগ্ন হতেন, আমাদের তাড়া লাগাতেন বাবাকে ডাকার জন্য। মা’র ঐ উদ্বিগ্নতাটুকু বড় ভালো লাগত। বাবা ধীরে সুস্হে সিগারেটটা শেষ করে যেই না ট্রেনে লাফিয়ে উঠতেন, তখনি মনে হতো ঠিকমত ট্রেনটা চলতে শুরু করত। বাবা মৃদু বকা খেতেন মা’র কাছে তাঁর অর্বাচীন কাজের জন্য।
ততক্ষণে চারদিক ফর্সা হয়ে গেছে। দেখতাম, সোনার থালার মতো সূর্য্যটা লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে। আমরা জানালার ধারে বসে টেলিগ্রাফের খুঁটি গুণতাম, মাইল ফলক দেখতাম এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতাম কি বলছে ট্রেনটা - ‘যাচ্ছি যাবো’ না ‘মন-পিয়াসা’? মিটার গেজের ঢিকঢিকিয়ে চলা গাড়ীর ইঞ্জিন থেকে কয়লার গুঁড়ো এসে চোখে পড়ত। আমরা জানালার বাইরে মুখ বাড়ালেই জামায় টান পড়ত মা’র হাত। বাবা স্টেশন চেনাতেন - এটা হাজীগঞ্জ, এটা লাঙ্গলবন্দ।
একসময়ে ট্রেন এসে দাঁড়াত লাকসাম জংশনে। বড় স্টেশন। গাড়ী বদল করতে হতো। চট্টগ্রামগামী ট্রেন ধরতে হতো। একটা ট্রেনের নাম মনে আছে- ‘গ্রীন এ্যারো’। বাবা গিয়ে জলের বোতল ভরে নিয়ে আসতেন। একটা বিশালকায় উঁচু বাদামী রংয়ের জলের যন্ত্র ছিল মনে আছে। সারা জংশনে বেশ কিছু ইঞ্জিন ফোঁসফোঁস করত। একসময়ে মা’র এক দূরসম্পর্কের মামা ঐ জংশনের স্টেশন মাস্টার ছিলেন- বিশাল ব্যাপার। ঐ সময়ে যতবার আমরা গেছি, আমাদের সেই নানা (মা তাঁকে শেখু মামা বলে ডাকতেন) আমাদের বগিতে এসে মা’সহ আমাদের সবাইকে স্টেশনের বিশ্রামাগারে নিয়ে যেতেন। সাদা কাপড় দেয়া টেবিলে উর্দিপরা পরিবেশকের চা আর অন্যান্য খাবার পরিবেশন করতেন আমাদের। গার্ড সাহেব আসতেন- তাঁর শোলার টুপিটা খুলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। আমাদের ছোটদের অবশ্য সবচেয়ে প্রিয় ছিল বেতের সেই বিশালকায় আরাম কেদারা। আমরা সেটায় উঠে শুয়ে থাকতাম।
তারপর আবার যাত্রা শুরু। সূর্য্য ততক্ষণে আস্তে আস্তে এলিয়ে পড়তে শুরু করেছে। ট্রেনের পাশের গাছপালার ছায়া পড়তে শুরু করত রেলপথের ওপর। কলাগাছের সারির ফাঁক দিয়ে সূর্য্যরশ্মি দেখা যেত। রেলপথের পাশের ছোট ছোট জলাশয়ের ওপর পানাগুলো চিক চিক করত। আমরা ছোটরা ততক্ষণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। টেলিগ্রাফের তারে বসা ফিঙে পাখীর লেজ ঝোলানো আর ভালো লাগছেনা। ট্রেনের চাকার শব্দ কি বলছে তা’নিয়ে আর কোন তর্ক নেই। মা-বাবাকে শুধু একটাই প্রশ্ন - আর কতক্ষণ?
একসময়ে ট্রেনটা ফেনী স্টেশনে এসে আস্তে আস্তে ঢুকত। মা-বাবা সবকিছু গোছগাছ সেরে নিয়েছেন। মা উৎসুক চোখে বাইরে তাকিয়ে থাকতেন। ঐ তো দেখা যেত কানা মামা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের দেখতে পেয়ে হাত নাড়ছেন। মা’র সারামুখে একটা গর্বের আভা- বাবার মুখে স্মিত হাসি। আর আমরা? ঘুমে ঢুলু ঢুলু।
তারপর? না, তার আর পর নেই এ মুহূর্তে। কোথায় ফেনী? এতো দাঁড়িয়ে আছি লন্ডনের বাড়ির বারান্দায় পাঁচ দশক পরে। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, এ তাড়া আর বিশ্বায়ণের যুগে ওরকম পরিবারিক সম্মিলনী হয়তো ঘটে কালে ভদ্রে বহুকাল পরে একবার, হয়তো নিজ দেশে নয়, ভিন্ন কোন দেশে।
সময়ের স্বল্পতা আর কাজের তাড়ায় সম্মিলনীতে সত্যিই কি মিলিত হতে পারি? সম্মিলনীর এ স্বল্পকালেও কে কাকে কতটুকু সময় দিতে পারি? দাপ্তরিক কাজ তাড়া করছে আমাদের সবাইকে তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে। পালাবার পথ নেই। আর প্রযুক্তিকে দুষেই বা কি হবে? আমরা নিজেরাই তো এ প্রযুক্তি আর সামাজিক মাধ্যমের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছি। মুঠোফোন তো আমাদের জীবন-যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। দু’ মিনিট পরপরই খুলছি দেখতে নতুন কিছু এলো কি না, যদিও ভালো করে জানি, ঐ দু’মিনিট মুঠোফোন না খুললে আমাদের কিংবা পৃথিবীর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।
অন্যদিকে বৈশ্বায়ণের কালে পৃথিবীর নানান দেশে ছড়িয়ে আছি আমরা সবাই অনেকটা বিশ্ব নাগরিকের মতো, সবার একসঙ্গে হওয়া এক বিরল ঘটনা বটে - সবার কাজ, ছুটি আর অগ্রাধিকার মেলানো এক কসরত বটে। কত যে বার্তা চালাচালি, মুঠোফোনে কথা বলাবলির পরে শেষ পর্যন্ত একটা অভিন্ন সময় বার করা গেছে। সুতরাং ‘মেলাবেন, তিনি মেলাবেন’ বলে অমিয় চক্রবর্তী যতই আমাদের আশ্বস্ত করুন না কেন, মেলানো নিতান্ত সহজ কাজ নয়।
এনএস/
