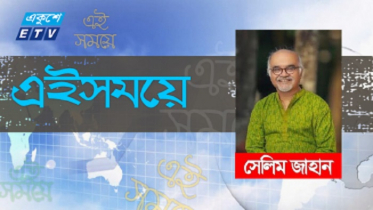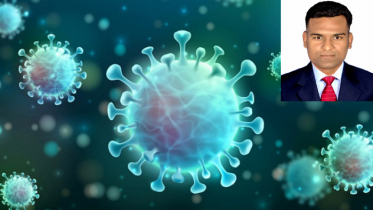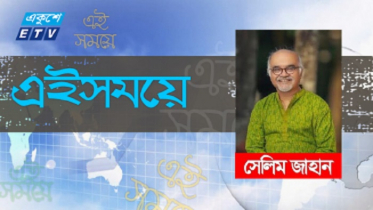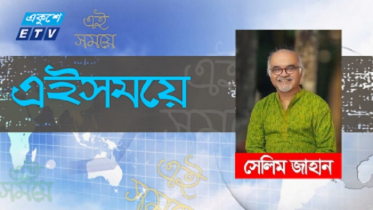আমার স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ
প্রকাশিত : ১৯:২২, ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ | আপডেট: ১৯:২৫, ১৭ ডিসেম্বর ২০২০

আমার বয়স তখন সাড়ে পাঁচ হবে। স্কুলে যাওয়া শুরু করিনি। ছোটবেলা থেকেই আমি কথা বলতে এবং অন্যের কথা শুনতে পছন্দ করতাম বলে ঘরের লোকজন আমাকে মানুষের মধ্যে গণনা না করলেও ঘুরে ঘুরে কে কী করছে, বলছে তার মোটামুটি সব খবরই রাখতাম বৈকি!
তেমনি ৭০-এর নির্বাচনের পূর্বে প্রায় দিনই সন্ধ্যায় দেখতাম- আমার মেজদা, সেজদা দুই ভাই বড়ো বড়ো অক্ষরে প্ল্যাকার্ড, পোস্টার, ব্যানার লিখত, নৌকার ছবি আঁকত। কারটা কেমন হলো- তা নিয়ে দুজনে মাঝে মাঝে তর্কাতর্কিও করত।
প্রতিদিনই দেখতাম- আমাদের বাড়ির অনতিদূরে আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তার পথ ধরে অনেক লম্বা মিছিল যাচ্ছে। দাদাদের কাছে শুনতাম- তারাও নাকি স্কুল-কলেজ থেকে মিছিলে যোগ দিত। "তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা", 'ভোট দিন, ভোট দিন, নৌকা মার্কায় ভোট দিন'- মিছিলের শ্লোগানে আরও অনেক কিছু তারা বলত, যা আজ আমি মনে করতে পারছি না।
৭ ডিসেম্বর ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একচেটিয়া বিজয় লাভের পরে দিন যতই যেতে লাগল দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ততই অবনতির দিকে যাচ্ছিল। প্রায়দিনই দেখতাম- বাবা তার মুদি দোকান থেকে উদ্বিগ্নমুখে ঘরে ফিরে দেশের ভয়াবহ অবস্থার কথা অর্থাৎ কোথায় কী হচ্ছে বা ঘটছে- সে সব কথা মা ও অন্যান্য সদস্যদের কাছে বলতেন। ঘরের মধ্যে সবার মনেই ছিল উদ্বেগ আর অজানা ভয়-ভীতি।
আমার কাছে কেউ কখনও এসব কথা বলেনি। তবুও কথাপ্রিয় আমি ঘুরে ফিরে সবার কাছে বিশেষ করে আমার শ্রুতিধর, গল্প বিশারদ আট বছর বয়সী ছোটদির কাছে সম্ভাব্য পাকিস্তানি আক্রমণ, যুদ্ধ এসব সম্পর্কে অগ্রিম যা শুনেছিলাম তা এতটাই ভয়াবহভাবে আমার মনের মধ্যে আঁকা হয়েছিল যে, আজও তা হুবহু মনে করতে পারি। আর মনে পড়লে গায়ের লোমগুলো আজও দাঁড়িয়ে যায়।
২৫ মার্চের কালো রাতে শুরু হলো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরিকল্পিত গণহত্যা। অসংখ্য মানুষের, বিশেষ করে- রাজনৈতিক ও সামরিক শাসন বিরোধীদের রক্তে রঞ্জিত হলো ঢাকার রাজপথ, অলিগলি, বাড়িঘর, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো। ২৬ মার্চ থেকে রেডিওতে বারবার শোনা গেল 'স্বাধীন বাংলাদেশের' ঘোষণা আর মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বাঙালিদের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের সেই উদাত্ত আহ্বান- 'এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম- স্বাধীনতার সংগ্রাম, তোমাদের যার যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো'।
পাকিস্তান থেকে প্লাটুনে প্লাটুনে মিলিটারি আসতে লাগল। দেশের বড়ো বড়ো শহরগুলোতে দ্রুতবেগে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন ভয়ে তাদের শহরের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে আমাদের গ্রামের বাড়িতে এসেছিল। ফলে আমাদের পরিবারের লোকসংখ্যা ষোলোজন থেকে বেড়ে পঞ্চাশ জনের মত হলো। এদের কেউ কেউ রাতে আমাদের প্রতিবেশিদের বাড়িতে ঘুমাতো আর খাওয়া দাওয়া আমাদের বাড়িতেই হতো। গ্রামাঞ্চল বলে আমাদের এলাকায় মিলিটারি আসতে কিছুদিন সময় নিয়েছিল।
বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের আধিক্যের কারণে আমার খেলার সাথীর সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেল। লেখাপড়া যা একটু শুরু হয়েছিল তা-ও বন্ধ হয়ে গেল। খেলাধুলা চলছিল অপ্রতিহত গতিতে। কয়েক মাস ধরে মিছিল দেখতে দেখতে আমাদের পছন্দের খেলাটাও ছিল মিছিল মিছিল খেলা। বিকেল হলেই ছোটরা সবাই মিলে উঠোনে মিছিলের মতো লাইন করে দাঁড়িয়ে চিকন বাঁশের লাঠি বা মোটা পাটকাঠির মাথায় যে কোনও কাপড় বেঁধে বড়ো উঠানের এক প্রান্ত থেকে বাড়ির ভিতরের আশেপাশের পথগুলোতে ছুটে ছুটে দৌড়াতাম আর মুজিবর মুজিবর বলে চিৎকার করতাম।
আমার ছোট বোন তখন মুজিবর বলতে পারত না। সেও পতাকার অনুকরণে ছোট এক টুকরো লাঠি নিয়ে দৌড়াত আর বলত মুদিবর, মুদিবর। আমাদের প্রতিবেশি মধ্যবয়সী কিরণ পিসিও কেনো জানি না মুদিবর বলত। আর সবাই তাই নিয়ে হাসাহাসি করত।
বাড়িতে সকাল সন্ধ্যায় রেডিওতে শুধু বিবিসি, ভয়েজ অব আমেরিকা আর সবচেয়ে বেশি শোনা হতো- দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গম্ভীর কণ্ঠের আকাশবাণী কলকাতার খবর, যার বেশিরভাগই ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে। আমাদের আশেপাশের প্রতিবেশিদের কারও বাড়িতে তখন রেডিও ছিল না বিধায়, তারাও প্রতিদিন সকালে না আসলেও বিকেলে আসতো আমাদের বাড়িতে খবর শুনতে।
অনেক লোকের সমাগমে উঠানটা তখন গমগম করতো। খবরের পাশাপাশি সবাই অপেক্ষা করতো স্বাধীন বাংলা বেতারের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান বিশিষ্ট লেখক এম আর আখতার মুকুলের রচিত এবং উপস্থাপিত 'চরমপত্র' শোনার জন্য। এই 'চরমপত্র' ছিল পাক-বাহিনীর প্রতি ব্যাঙ্গাত্মক ও শ্লেষাত্মক মন্তব্যে ভরপুর আর মুক্তিযোদ্ধা ও সকল শ্রেণির বাঙালির আত্ম-মনোবল বাড়াতে মহৌষধের মতো।
দেখতাম- এই চরমপত্র শোনার পরে সবাই আনন্দে সারাদিনের দুঃখ-কষ্ট ভুলে যেত। রেডিওতে আরও শোনা যেত- উদ্দীপনামূলক গান, যা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস আর সাধারণ মানুষের মনে আশার সঞ্চার করত। যেমন- 'জয় বাংলা বাংলার জয়', 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবো রে' -এরকম আরও কিছু গান। সবাই মনোযোগ দিয়ে এসব গান উপভোগ করত। প্রতিদিন সবার জন্য সন্ধ্যায় পান-তামাকের আয়োজনও থাকত। তখন চায়ের প্রচলন ছিল না তেমন গ্রামে।
দিনদিন দেশের অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকলো। আমাদের গ্রামে এবং আশেপাশের গ্রামগুলোতে পাকিস্তানি মিলিটারি এসে পড়লো। একদিন ভোর রাতে আমার সেজ'দা কাদের সঙ্গে যেন কোথায় চলে গেল। আমি টের পেয়েছিলাম, কিন্তু কোথায় তা জানতাম না। বড়ো হয়ে জেনেছি- সে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিতে ভারতে গিয়েছিল।
আমাদের বাড়ি থেকে পূর্ব দিকে দুই ঘর পরের এক বাড়ির লোকদের তাড়িয়ে শান্তি কমিটির লোকেরা সেখানে থাকতে শুরু করল। প্রায়ই তারা চাল-ডাল, খাসি, হাঁস বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চেয়ে আমাদের বাড়িতে লোক পাঠাত আর বিনিময়ে আশ্বাস দিয়ে বলত- "ভয় নাই, আপনাদের কিছু হবে না। আপনাদের মূল্যবান জিনিসপত্রও আমাদের ঘরে রাখতে পারেন।" তাই আমাদের ঘর পুড়ে যাওয়ার আশংকায় বাবা কিছু শীতের পোশাক আর দলিলপত্র রেখেওছিল তাদের ঘরে।
আমাদের গ্রামের পাশেই সন্ধ্যা নদী। একটু বেলা হতেই অর্থাৎ ৯টা, ১০টার দিকে প্রায়ই এ নদীতে মিলিটারির গানবোটের শব্দ শোনা যেত। এই শব্দ কানে আসার সাথে সাথে ঘরের সব লোকজন, আশ্রয়প্রার্থী আত্মীয়-স্বজন সবাই যে যার অবস্থায় থাকতো, জঙ্গলে পালাতে ছুটত। শুনতাম- আজ এর বাড়ি, কাল ওর বাড়ি, মানুষের দোকানপাট সব পুড়িয়ে দিচ্ছে মিলিটারিরা, আর ঘরের মেয়ে-বউদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্পে। পুরুষদের ধরে সেই নদীর ধারে সারিবদ্ধ করে এক গুলিতে মেরে নদীতেই ফেলে দিত। প্রায়ই লাল হয়ে যেত সন্ধ্যা নদীর জল।
মা খুব সকালে উঠেই অনেক বড়ো একটা হাঁড়িতে ভাত রান্না করতো। সবাইকে সকালে খাওয়াত আর বলতো- পেট পুরে খাও, আবার কে, কখন খাবে কে জানে! প্রতিদিন একই নিয়মে সবাই খেয়ে-দেয়ে তৈরি হয়ে চাকরিতে যাওয়ার মতো করে ঘর থেকে বেরিয়ে পালাতে যেত। মনে পড়লে হাসি পায় আজও। যাওয়ার আগে ঘরের বয়স্ক সদস্যরা, বিশেষ করে- আমাদের মামা (যিনি আমাকে ডাকতো- টিয়াপাখি) জিজ্ঞেস করত- বলতে পারো টিয়াপাখি, আজ মিলিটারি আসবে কি আসবে না?
আমি মাথা ঝুলিয়ে হ্যাঁ বা না কিছু একটা বলে দিতাম। আর আমার ভীতু সব গুরুজনেরা তা-ই বিশ্বাস করত। তারা বলতো- ছোটদের মধ্যে ভগবান থাকে, ওরা যা বলে তা-ই ঠিক হয়। এ কারণে এই ক্ষুদে ভবিষ্যৎ বক্তাকে পালাতে যাওয়ার আগে সবাই দেবজ্ঞানে খুব ভক্তি-সম্মান করত। আমি মিলিটারি আসবে না বললে তাদের পালাতে যাওয়ার ব্যস্ততা কমে যেত, আর আসবে বললে তাড়াতাড়ি দৌড়াত। প্রায়দিনই আমার আন্দাজি বলা ঠিক হতো বলে তাদের বিশ্বাসও বেড়ে গেল।
সবাই পালাতে চলে গেলে মা আবার এক হাঁড়ি ভাত রান্না করে ঘরের পিছনে কাকরোল গাছের ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে রাখত। কাঁসার থালা বাসনগুলো কিছু পুকুরের পানিতে আর কিছু সেই কাকরোল গাছের ঝোপের মধ্যে লুকাত। ঘরের কিছু চাল-ডাল বাবা একটু দূরে গোপন জায়গায় মাটির নিচে মজুদ রেখেছিলেন। লোকজন জঙ্গলে পালিয়ে আর জিনিসপত্র লুকিয়ে রেখে প্রতিদিনই যেন মিলিটারিরা আসবে বলে ঘরটা তৈরি করা হতো। সে এক দুর্বিষহ অনুভূতি!
আমার মা কোনওদিন ঘর ছেড়ে পালাননি। আমাদের মামা অনেক বয়স্ক ছিলেন আর তার ভয়ও ছিল খুব বেশি। বড়দারও খুব ভয় ছিল। এই দুই ভীতু লোক 'মামা-ভাগ্নে যেখানে আপদ নেই সেখানে' -এই বিশ্বাসে প্রতিদিন একত্রে পালাতে যেত। আমার বড়দিদি ও আরও দুই তিনজন আত্মীয় বড় মেয়েকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিদিন পালাতে হতো। কারণ তাদের মরার চেয়েও ধরা পড়ার ভয় বেশি ছিল। বড় বউদি তার ছোট ছোট তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে বাড়ির কাছাকাছি জঙ্গলে পালাতে যেত। মাঝে মাঝে তার সাথে আমার বড়দি ছোড়দিও যেত।
পুরুষেরা পূর্বেই ঘরের বউ-ঝিদের জন্য সময় সুযোগ মতো জঙ্গলের ভিতর কেটে দুই তিনটা জায়গা সুন্দরভাবে বসার উপযোগী করে রাখত। বউদির সাথে আমিও গিয়েছিলাম প্রথম দিন। কিন্তু এ পালানোর মর্ম ঠিকমতো উপলব্ধি করতে না পারায় অর্থাৎ- এ পালানোকে লুকোচুরি খেলা মনে করে নিষেধ সত্ত্বেও কু-উ-উ-ক, কু-উ-উ-ক করে শব্দ করেছিলাম বলে আমাকে আর কেউ পালাতে নিতে সাহস পেত না।
বউদি বসার জন্য তার সাথে মাদুর, বিছানা, হাত পাখা আর ছেলেমেয়েদের চুপ রাখার জন্য আম, মুড়ি, দুধের বোতল আরও অনেক খাবার খাদ্য নিয়ে যেত। তারাও খাবার ফুরিয়ে গেলেই কান্নাকাটি, শব্দ, চিৎকার শুরু করে দিত। তাই মাঝে মাঝে বউদিও রেগে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়ি চলে আসত।
আমি, আমার মা আর ছোট বোন- এ ক'জন সবসময় ঘরেই থাকতাম। এছাড়া কেউ অসুস্থ হলেও তারা ঘরে থাকত মায়ের তত্ত্বাবধানে। প্রতিদিন একই নিয়মে সবাই পালাতে যেত। আর আমি, একদিকে মিলিটারি নামক কল্পিত দানবের আক্রমণ আশংকা অন্যদিকে মা না গেলে আমিও অন্য কারও সাথে পালাতে যেতে পারছিনা- এই দুয়ের মাঝে প্রতিদিনই ভয়ে শক্ত হয়ে সামনের বারান্দায় এসে জানালা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতাম।
এক এক দিন দেখতাম- দূরের আকাশ আগুনে লাল হয়ে গেছে, আশেপাশে ধোঁয়া উড়ছে, আবার কখনও অনতিদূরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। চারদিক থেকে চাল, ডাল,খই, মুড়ি পোড়া গন্ধ আসছে, কারোর ঘরের টিন ছুটে যাওয়ায় ঠাস ঠাস শব্দ হচ্ছে। আমি এর মাঝে ভীত চোখ আর মন নিয়ে সারাক্ষণই কোনও মন্ত্র-তন্ত্র নিয়ম ছাড়া যা মনে আসত, তাই বলে আমার ঈশ্বরকে ডাকতাম। শুধু বলতাম- হে ভগবান, মিলিটারি যেন আমাদের বাড়ি না আসে, আমাদের ঘরটা যেন খুঁজে না পায়। এ ঘরটা পুড়ে ফেললে আমি দাঁড়াব কোথায়?
এরপর একদিন দেখলাম- বাড়ি থেকে অনতিদূরে আমাদের পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস বাবার মুদি দোকানটাও জ্বলছে দাউ দাউ করে। গন্ধ পেলাম দোকানের রকমারি জিনিস পোড়ার আর সাথে পুড়ে গেল আমাদের বৃহৎ যৌথ পরিবারের ভবিষ্যৎ স্বচ্ছলতাটুকুও। আমি বুঝেছিলাম- এটা আমাদের দোকানই ছিল। আর একটু পরে জ্বলতে দেখলাম আমাদের প্রতিবেশির খড়ের গাদা। আমি ভয়ে শক্ত হয়ে শুধু নিঃশব্দে একা একা কাঁদছিলাম। সেদিন আমি যে ভয় পেয়েছিলাম তার সাথে জীবনে পাওয়া অন্য কোনও ভয়ের তুলনা চলে না।
কিছুক্ষণ পরে দেখলাম- আমাদের বাবা কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে এলেন বাড়িতে। চিৎকার করে মায়ের নাম ধরে ডেকে বললেন- আমি নেভাতে পারিনি, শুধু গাছের আড়াল থেকে চেয়ে চেয়ে দেখেছি। আমার এত বছরের দোকানটা ওরা আনন্দ করে পুড়িয়ে দিচ্ছে। ওদের সাথে আমাদের দেশি লোকও ছিল। তাদের মুখে শুনেছি- আমার নাম বলতে, আবার তারাই আমাদের বাড়ির পথের অর্ধেকটা এসেও অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। খুব সম্ভবত সেই শান্তি কমিটির লোকজনই হবে।
শিশুদের কাছে বাবা হচ্ছেন সুপার হিরোর মতো। তাই আমাদের দোকানটা পুড়িয়ে দেওয়ার পরে জীবনে প্রথমবার বাবাকে কাঁদতে দেখে দুঃখ-কষ্ট-ভয় মিলে কেমন লেগেছিল সেদিন। তা আমার জানা কোনও শব্দ বা বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যাহোক, আমাদের বাড়িটা সেদিন বেঁচে গিয়েছিল।
প্রতিদিন সকালে যারা পালাতে যেত আর সন্ধ্যায় ফিরে আসত- তা ছিল ঠিক যেন চাকরির ৯টা-৫টা ডিউটির মতো। তবে পালানোর এ ডিউটি থেকে ফেরার পরে সবার চেহারাই পাল্টে যেত। ফিরে একজন আর একজনকে খুঁজতো, দেরি হলে এই বলে চিন্তা করত যে- কিছু হলো না তো আবার! সবাই একত্রিত হলে সেদিনের মতো সবাই খুব খুশি হতো। সন্ধ্যায় প্রথমে গল্প হতো কে, কোথায়, কতদূরে, কোন জঙ্গলে বা পেয়ারা বাগানে পালিয়েছিল, কে কতদূর থেকে মিলিটারি যেতে দেখেছে, কে একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছে, রাস্তার পাশ দিয়ে মিলিটারি যেতে দেখে ভয়ে কার পানিতে ডুব দিয়ে থাকতে থাকতে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে; এরকম আরও কত গল্প শুনেছি।
আর আমরা এমন কিছু দেখতাম- যা তারা নিজেরা দেখতে পেত না। যেমন- কারও গায়ে বড়ো বড়ো জোঁক রক্ত খেয়ে ঢোল হয়ে লেগে আছে, কারোর ঠোঁট পানিতে থাকতে থাকতে সাদা হয়ে গিয়েছে, কারও গায়ে কাঁটার খোঁচায় বের হওয়া রক্ত শুকিয়ে আছে। সবাই এক রাতের মতো খুশি মনে একত্রে খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাতো। বিকেলের পরে আর মিলিটারি আসার ভয় থাকত না গ্রামে। সকাল হলে আবার যথানিয়মে শুরু হতো বড়োদের লুকোচুরি খেলা। তাই সবাই আলোর চেয়ে আঁধার অর্থাৎ দিনের চেয়ে রাতকেই বেশি পছন্দ করত তখন।
মিলিটারিরা জেলেদের বাড়ি পোড়াত না, কৃষকদেরও বেশি মারত না। তাই জেলে না হয়েও অনেকে বাড়ির সামনে জাল টাঙিয়ে রাখত। কৃষক না হয়েও জঙ্গলে না পালিয়ে মাঠে কাজ করত। খাঁটি মুসলিমদের ওরা বেশি মারত না- এই বিশ্বাসে গ্রামের অনেক হিন্দুরাও সাথে টুপি রাখত আর চার কলেমা মুখস্থ করত। কাছাকাছি মিলিটারি দেখলে টুপি মাথায় দিত আর কলেমা পড়তে থাকত। মাঝে মাঝে কেউ ধরা পড়ে গেলে টুপি মাথায় থাকলেও ওদের সন্দেহ হলে প্যান্ট খুলে হিন্দু না মুসলিম পরীক্ষা করে দেখত। আর কলেমা তৈয়বা পড়তে বলত। সে ক্ষেত্রে হিন্দু প্রমাণ হলে তো গুলি করত সাথে সাথে আর মুসলিমরাও ভয়ে কলেমা পড়তে ভুল করলে রাইফেলের বাট দিয়ে মারত, কখনও তাদেরও গুলি করত। আমাদের ঘরেও বেশ কিছু টুপি সংগৃহিত ছিল সে সময়।
বাবা সন্ধ্যা হলেই বাজারে গিয়ে বড়ো বড়ো মাছ, বিশেষ করে- মনে পড়ে কালিবাউশ মাছ, নদীর তাজা তাজা ভিন্ন জাতের মাছ আনতেন। আর বলতেন- কখন, কে মারা যাই বলা তো যায় না। তাই যতক্ষণ বাঁচি খেয়ে নাও সবাই। সম্ভাব্য মৃত্যুভয়ে রাতে খাওয়া দাওয়া খুব ভালোই হতো তখন।
দিন যতই যেতে লাগল গ্রামের মানুষ ততই পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে অভ্যস্ত হতে লাগল। প্রথম দিকে যেমন সবাই বুঝে না বুঝে পালাত, তিন চার মাস পরে আর তেমন ভয় করত না। গ্রামবাসী আস্তে আস্তে মিলিটারির গতিপথ, আসা যাওয়ার সময় বুঝতে ও শিখতে শুরু করল। অনেক ছোট-বড় পোল, সাঁকো ভেঙে ফেলা হলো- যাতে সহজেই মিলিটারিরা আক্রমণ করতে না পারে। তাছাড়া সন্ধ্যা নদীতে গানবোটের শব্দ পেলে বা কোথাও রাইফেলের গুলির শব্দ পেলে সেই অনুযায়ী মানুষ নিজেকে লুকিয়ে ফেলত। শব্দের প্রতি মানুষের এমন ভয় ছিল যে, পালানোর শেষে বাড়ি ফিরে কেউ যদি একটু জোরে কাপড় কাচার শব্দও শুনতে পেত, তাইলেও আবার দৌড়ে পালাত।
আমাদের প্রতিবেশি কিরণ পিসি ছিল সেই সময়ের স্থানীয় চলন্ত সংবাদমাধ্যম। যেহেতু এটা তার বাবার বাড়ি আর সবাইকেই সে ভালোবাসত, তাই যে কোনও ঘটনা ঘটলেই সে দ্রুত গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে খবর ছড়িয়ে দিত। সে যে কোনও সুখের বা দুঃখের ঘটনা যা-ই হোক না কেন। এজন্য তাকে সবাই ডাকতো রেডিও, ইত্তেফাক, রয়টার- এসব নামে। সে ছিল গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী। সবার বিপদে আপদে এমনভাবে সে ঝাঁপিয়ে পড়ত, যা অনেক ভদ্রবেশী পুরুষরাও করতে পারত না।
সে-ই হঠাৎ করে খবর দিত- নদীতে মিলিটারির গানবোট এসে গেছে, সবাই পালাও। সবাই হয়তো শুনতে পেত গানবোটের শব্দ, তবুও যাতে কেউ ভুল করে ঘরে বসে না থাকে তাই সবাইকে সে সজাগ করে দিত তার সাধ্যমত। তার কাছেই মাঝে মাঝে শোনা যেত- মুক্তিবাহিনীর গ্রেনেড হামলায় মিলিটারির গানবোট ডুবে যাওয়ার সংবাদ। নদীতে শত শত সাধারণ মানুষের লাশের মধ্যে মিলিটারির লাশও ভাসতে দেখা গিয়েছে- কিরণ পিসিই এসব খবর দিত।
মুক্তিবাহিনী ছিল সে সময় আমাদের একমাত্র আশার আলো, প্রার্থনায় ঈশ্বরের অবতারের মতো। এমন একজন মুক্তিযোদ্ধার নাম জেনেছি এ বছরে আমার পরিচিত এক ভাইয়ের "বরিশালের কৃতিসন্তান" শিরোনামে লেখা ফেসবুক পোস্ট থেকে। সেই মহিয়সীর নাম আলমতাজ বেগম ছবি। যিনি বর্তমানে পাথরঘাটায় নিজ গ্রামে ক্যান্সারে ধুঁকে ধুঁকে দিনাতিপাত করছেন।
ঊনপঞ্চাশ বছর পরে তার নিজের উক্তিতে তিনি যা বলেছেন, আর আমি পড়ে জেনেছি তা হলো- 'তিনি ছিলেন তখন নবম শ্রেণির ছাত্রী। তার মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের প্রেরণায় তিনিও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তার ভাষ্যমতে, তিনি সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে সন্ধ্যানদীতে পাকিস্তানি মিলিটারির গানবোটে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন গানবোট। আর মেরেছিলেন মিলিটারিদের কয়েকবার বিভিন্নস্থানে।
আমি ফেসবুক পোস্টের সেই লেখাটা পড়তে পড়তে সহসাই চলে গিয়েছিলাম ঊনপঞ্চাশ বছর আগের সেই শৈশবে, যখন প্রায়দিনই গানবোটের শব্দে ভয়ে কাঁপতাম, কাঁদতাম আর প্রার্থনা করতাম মিলিটারির ধ্বংসের জন্য। এদের মতো সাহসী নারী-পুরুষই সেদিন সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত দূত হিসেবে এগিয়ে এসেছিলেন আমাদের কান্না মোছাতে। তার কথা পড়তে পড়তে আমার চোখ জলে ভরে গেল কৃতজ্ঞতায়। মনে হলো- হয়তো তিনিই সেদিন আমাদের ঘরটা বাঁচিয়েছিলেন।
তিনি আরও বলেছেন যে, তিনি তখন পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পাননি। কেনও তা আমি জানিনা, তবে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি সেজন্যও। সত্যি বলতে কী, তাঁর ভয়ংকর কষ্টদায়ক ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন কাহিনী- যা তিনি মেয়ে হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে তৈরি হয়েছিল- তা শুনে আমি অনেকক্ষণ কেঁদে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি মনে মনে। আর ভেবেছি, বেঁচে আছেন বলেই কি তিনি মুক্তিযোদ্ধার সম্মান পেলেন না? কি কারণ, আমি জানি না। তবে তাঁর প্রতি এবং তাঁর মতো সকল জীবিত এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা চিরকালের।
এভাবেই অসংখ্য ভয়াবহ নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের কেটে গেছে মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস। অবশেষে হিংস্র পাক-বাহিনীর নারকীয় অত্যাচার থেকে মুক্তি মিলল ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর, ভারতের মিত্র বাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর কাছে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পনের মাধ্যমে। আমরা পেলাম একটা স্বতন্ত্র, স্বাধীন ভূখণ্ড, লাল-সবুজের একটা পতাকা আর সেই পতাকাকে সম্মান দেখানোর জন্য একটা স্বতন্ত্র জাতীয় সংগীত- 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'।
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বিশ্বের মানচিত্রে ভেসে ওঠা সেই নতুন ভূ-চিত্রটির নাম হলো বাংলাদেশ।
লেখক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী, শিক্ষক, ফেয়ারফেক্স কাউন্টি পাবলিক স্কুল।
এনএস/
** লেখার মতামত লেখকের। একুশে টেলিভিশনের সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে।