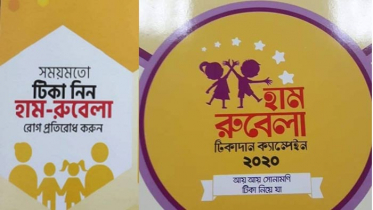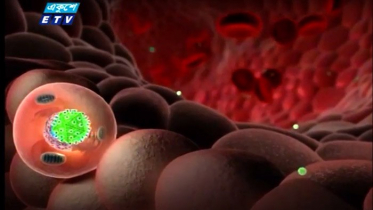ইনসুলিন: ইতিহাসের বাঁক বদলে দিয়েছিল যে আবিষ্কার
প্রকাশিত : ১১:১৫, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু দুশ্চিন্তা জড়িয়ে থাকে যে রোগটির সঙ্গে সেটি হলো ডায়াবেটিস। সব রোগের মূল বলা হয় একে। সারাজীবন বয়ে বেড়ানোর রোগও বটে। মুখে খাওয়ার ওষুধ থেকে শুরু করে হালের ইনসুলিন- চিকিৎসার নানা পদ্ধতিও এর পুরোপুরি নিরাময়ের পথ দেখাতে পারেনি। তবে ইনসুলিন এই রোগের চিকিৎসার রূপ ব্যাপকভাবে পাল্টে দিয়েছে। সেটা কীভাবে?
ধরুন আপনার ডায়বেটিস হয়েছে। ডাক্তার আপনাকে পরামর্শ দিলেন, প্রতি সপ্তাহে একটা করে গরুর অগ্ন্যাশয় কাঁচা চিবিয়ে খাবেন। আপনি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তারের দিকে, ডাক্তারও আপনার দিকে তাকিয়ে রইলেন মহাবিরক্ত হয়ে। ডাক্তারের বিরক্তির কারণ হলো- কিছুক্ষণ আগেই আপনার প্রস্রাব চুমুক দিয়ে চেখে আপনার ডায়বেটিস শনাক্ত করেছেন তিনি!
এমন দৃশ্য এখন কষ্টকল্পনা হলেও, ১৯২১ সালের আগে দশা অনেকটা এরকমই ছিল। তখনকার দিনে ডায়বেটিস রোগীরা এক কি দুই বছরের বেশি বাঁচত না। মৃত্যুর হার ছিল শতভাগ। কারণ এই রোগের কোনো প্রতিকার জানা ছিল না কারো। সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা ছিল কঠিন ডায়েট- ন্যূনতম কর্বোহাইড্রেট গ্রহণ। হয়তো সারাদিনে মাত্র ৪৫০ কিলোক্যালোরি। এক স্লাইস পিজ্জা বা দুটো চিকেন ফ্রাইতে এর চাইতে বেশি ক্যালরি থাকে। এতে করে বাঁচার জন্য অতিরিক্ত কয়েক বছর পাওয়া গেলেও, শেষমেশ বাঁচতনা কেউই। অনেকে তো এই কঠিন ডায়েটের কারণে অনাহারেই মারা পড়ত। হাসপাতাল ভরে থাকত মৃত্যুপথযাত্রী ডায়বেটিস রোগী দিয়ে।
এই দৃশ্য রাতারাতি বদলে দিল যে আবিষ্কার, সেটা হলো ইনসুলিন। ১৮৮৯ সালে জার্মান গবেষক অস্কার মিনকোওস্কি আর জোসেফ ফন মেরিং দেখেন যে, কুকুরের অগ্ন্যাশয় কেটে দিলে, সেটার ডায়বেটিসের লক্ষণ দেখা দেয় এবং সেটা মারা যায় কয়েকদিন পরেই। এখান থেকেই ধারণা করা হয় যে অগ্ন্যাশয় হলো সেই উৎস যেটা থেকে কোনো একটা বস্তু বের হয়, যা শরীরে ডায়বেটিস হতে বাধা দেয়।
পরবর্তীতে ইউজিন ওপিক দেখান যে, পুরো অগ্ন্যাশয় না বরং এর ভিতরকার আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স নামের একটা বিশেষ কোষগুচ্ছই এজন্য দায়ী।তিনি দেখান যে, অগ্ন্যাশয় নষ্ট হলেও যদি আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স ঠিক থাকে, তাহলে ডায়বেটিস হয় না, বরং উল্টো ক্ষেত্রে হয়।
যে জিনিসটা এই কাজ করে তার নাম দেওয়া হয় ইন্টারনাল সাবট্যান্স। এবার সবাই মিলে শুরু করলেন এই জিনিসটা খোঁজা। কিন্তু কেউই সফল হচ্ছিলেন না। এই আবিষ্কারের পরেই মূলত রোগীকে অগ্ন্যাশয় খাওয়ানোর ব্যাপারটা শুরু হয়। মাঝে মাঝে অগ্ন্যাশয় বেটেও খাওয়ানো হতো, বা রস বের করে সেই নির্যাস খাওয়া হতো।
কারো কারো ক্ষেত্রে কাজও হতো, কিন্তু সেই সাথে ভয়ানক সব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও দেখা দিতো তাতে: বমি, জ্বর, খিঁচুনি, পেট খারাপ সহ আরও নানা উপসর্গ। অগ্ন্যাশয়ের রস বা নির্যাসের ইঞ্জেকশন ছিল আরো ক্ষতিকর।
কেউ কেউ বলতে লাগলো যে এই হাইপোথিসিস সম্ভবত ভুল।
তবে ১৯১০ সালে স্যার এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট শারপে দাবি করেন, স্বভাবিক লোকের তুলনায় ডায়াবেটিস রোগীর শরীরে শুধু একটা কেমিক্যাল নেই। এরপর যা হলো তাকে অভাবনীয়ই বলা যায়।
১৯২০ সালের ৩০ অক্টোবর রাতে নিজের ঘরে পড়াশোনা করছিলেন ইউভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অন্টারিওর শিক্ষক ফ্রেডরিক ব্যানটিং। পরের দিন ক্লাসে অগ্ন্যাশয়ের উপরে পড়াতে হবে তাকে। আগের নানা গবেষকদের আর্টিকেল পড়তে পড়তে মোজেস ব্যারনের লেখা ‘দ্য রিলেশন অব আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স টু ডায়াবেটিস’ নামের একটা আর্টিকেল তার চোখে পড়ে, যেখানে প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট ব্লকেজ এর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। মানে হলো অগ্ন্যাশয়ের রস আসে যে নালি দিয়ে সেই নালিকে আটকে দেওয়ার কৌশলের ব্যাপারে। লেখাটা ভাবনায় ফেলে দেয় ব্যানটিংকে। ভাবতে ভাবতেই একটা বুদ্ধি আসে তার মাথায়।
তিনি ধারণা করলেন, অগ্ন্যাশয় থেকে আসা পাচক রস বা খাদ্য হজমকারি রসটা সম্ভবত আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স থেকে আসা রসকে (ইন্টারনাল সিক্রেশন) নষ্ট করে দিচ্ছে।
উনি বুদ্ধি করলেন, যদি প্যানক্রিয়াটিক ডাক্টকে বন্ধ করে দেন, তাহলে অগ্ন্যাশয়ের বাকি সব অংশ শুকিয়ে যাবে, আর যে জিনিসটা থেকে যাবে, সেটা হলো আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স। আর সেখান থেকেই পাওয়া যাবে কাঙ্ক্ষিত ইন্টারনাল সিক্রেশন।
এই ধারণাটা নিয়েই উনি হাজির হন নিজের সাবেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইউভার্সিটি অব টরন্টোতে এবং সাহায্য চান জে জে ম্যাকলেয়ডের কাছে। তিনি স্কটিশ ফিজিওলজিস্ট। ওই সময়ের শীর্ষস্থানীয় ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ।
ফ্রেডরিক ব্যানটিং ও চার্লস বেস্ট
ম্যাকলেয়ডের সন্দিহান ছিলেন, ব্যানটিংয়ের ধারণা আসলেই কাজ করবে কিনা বা বুদ্ধিটা আসলেই তার কিনা। কিন্তু ম্যাকলেয়ড তখন ছুটিতে যাচ্ছিলেন, আর তার ল্যাবটা ফাঁকাই পড়ে থাকত। তাই সুযোগ দিলেন ব্যানটিংকে কাজের প্রমাণ দিতে, সেই সাথে সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে দেন পোস্টগ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট চার্লস বেস্টকে। কারণ বেস্ট রক্ত আর প্রস্রাবে সুগারের পরিমাণ মাপতে পারতেন।
ব্যানটিং এবং বেস্ট শুরু করেন কুকুরের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা। প্রায় ৪০০-৫০০ কুকুরের জীবন উৎসর্গ হয় এই গবেষণায়।
গবেষণা শুরু হয় ১৯২১ সালের ১৭ মে, আর জুলাই মাসের শেষের দিকে অবশেষে তারা নালি আটকে দেওয়া একটা কুকুরের অগ্ন্যাশয় থেকে একটা নির্যাস আলাদা করতে সমর্থ হন, যেটা কিনা একটা ডায়াবেটিক কুকুরকে ইনজেক্ট করলে দেখা যায় যে কুকুরটার ডায়াবেটিস কমে যাচ্ছে।
ডায়াবেটিসে আক্রান্ত কুকুরটা বেচে ছিলো প্রায় ৭০ দিন। নির্যাসটা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ার পরেই মারা যায় কুকুরটা। তাদের অন্যান্য সন্দিহান সহকর্মীরা এই নির্যাসের নাম দেন ‘থিক ব্রাউন মাক’ কিন্তু তখনো কেউ জানত না যে আসলে যা আবিষ্কার হতে যাচ্ছে তা একসময় কতো মানুষের জীবন বাঁচাবে।
ম্যাকলেয়ড ফিরে এসে তাদের গবেষণার ফলফলে খুশি হতে পারেননি। গবেষণাটি ছিল ভুলে ভরা, তারা যে কোনো নেতিবাচক ফলাফল বাদ দিয়ে যেতেন এবং স্পষ্টতই ফলাফলের ভুল প্রতিপাদন করছিলেন। ম্যাকলেয়ড তাই তাদরকে আর সহযোগিতা করতে চাচ্ছিলেন না, ফলে তাদের মধ্যে তিক্ততা তৈরি হয়। দুই গবেষকও ঝগড়া করে ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দেন।
ম্যাকলেয়ডের সন্দেহের আর একটা কারণ হলো ব্যানটিং ও বেস্ট পূর্বসূরি বিজ্ঞানীদের তুলনায় খুব বেশি আগাতে পারেননি। তাদের প্রকাশিত পেপারে অনেক কিছু লেখা থাকলেও, তাদের নোটবুকেই লেখা ছিল যে নির্যাসটা ঠিকমত কাজ করে না।
কিন্তু ১৯২১ এর ডিসেম্বরে দুই গবেষক হার মেনে নিতে বাধ্য হন। উপায় না পেয়ে, আবার ম্যাকলেয়ডের কাছে গিয়ে সাহায্য চান। ম্যাকলেয়ডের তত্ত্বাবধানে চলতে থাকে গবেষণা।
তারা এবার শুরু করেন গরু থেকে ইনসুলিন সংগ্রহ। মূল সমস্যা ছিলো নির্যাসটা সংগ্রহের পরে সেটাকে বিশুদ্ধকরণে, তাই তারা যোগাযোগ করেন বায়োকেমিস্ট জেমস কলিপের সাথে। তিনিও যোগ দেন দলে। প্রথমে তাদের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক থাকলেও সহসাই অবনতি ঘটে তাতে, কারণ কলিপ নিজেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন অনেকটা। ব্যানটিং ও বেস্টের অপরিশুদ্ধ নির্যাসটা নিয়ে কলিপ সেটিকে বিশুদ্ধ করার একটা উপায় বের করেন। বুদ্ধিটা হচ্ছে অগ্ন্যাশয়কে দেহ থেকে অপসারণের পরপরই ঠাণ্ডা করে ফেলতে হবে যাতে করে পাচক রসের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর পরিকল্পনা করা হয় জানুয়ারিতেই এই নির্যাসটা মানুষের উপর পরীক্ষা করার।
ব্যানিটং চাচ্ছিলেন, যা কিছু হয়েছে সেটার পুরো কৃতিত্বটাই যেন উনি পান, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। তাই উনি চাপ দেন যেন তার বের করা নির্যাসটাই প্রথম কারো উপরে প্রয়োগ করে দেখা হয়।
১৯২২ সালের জানুয়ারির ১১ তারিখে ব্যানটিং ও বেস্টের নির্যাসটা প্রথম প্রয়োগ করা হয়। লিওনার্ড থম্পসন নামের একটা ১৪ বছর বয়সী মুমূর্ষু বাচ্চাকে প্রথম দেওয়া হয় সেই ইঞ্জেকশন। কিন্তু ভয়ানক অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া হয় থম্পসনের। তাই পরে আর ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়নি। ডায়াবেটিস লেভেলও খুব একটা কমেনি না ওর।
কলিপ পরের কয়েকদিন দিনরাত খেটে তার নিজের বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া আরও উন্নত করেন। ব্যাপারটা ব্যানটিংকে জানানোর পরে উনি পদ্ধতিটা জানতে চান, কিন্তু কলিপ জানাতে অস্বীকার করেন। কলিপের কলার চেপে ধরেন ব্যানটিং। বেস্ট এসে ঠেকান।
১২ দিন পর, ২৩ জানুয়ারি দেওয়া হয় পরের ইঞ্জেকশন এবং এটা সফলতার সাথে ডায়বেটিসের সকল লক্ষণ কমিয়ে দেয়। সেই সাথে এর দৃশ্যত কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও ছিল না। থম্পসনের গ্লুকোজ লেভেল ২৮.৯ মিলিমোল পার লিটার (mmol/L) থেকে নেমে আসে ৬.৭ এ ।
কলিপই প্রথম তাই অগ্ন্যাশয়ের ইন্টারনাল সিক্রেশনের মিশ্রমন বানান, মানুষের ওপর যার সফল প্রয়োগ হয়।
যেসব বাচ্চা তখন ডায়াবেটিক কিটো এসিডোসিস এ (ডায়বেটিস অতিরিক্ত বেড়ে গেলে এই সমস্যা হয়) আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনত তাদেরকে রাখা হতো আলাদা একটা ওয়ার্ডে। মাঝে মাঝে ৫০ জনেরও বেশি হয়ে যেত রোগি। বেশিরভাগই থাকত কোমায় বা অজ্ঞান অবস্থায়।
থম্পসনের সফলতার পরে ব্যানটিং, বেস্ট ও কলিপ বেড থেকে বেডে গিয়ে নতুন বানানো নির্যাস ইঞ্জেকশন দিতে শুরু করেন। একে একে যখন তারা শেষ বাচ্চাটার কাছে পৌঁছান, তখন প্রথম ইনজেকশন দেওয়া বাচ্চাদের কয়েকজন কোমা থেকে জেগে ওঠে। এটা শুধু প্রতিষেধক ছিল না, ছিলো পুরো যুগান্তকারী সাফল্য। ইতিহাসের বাঁক বদলে দেওয়া ঘটনা।
এই দৃশ্যটা কল্পনার চোখে দেখলে দুনিয়ার তাবত সিনেমার গল্প হার মানাবে। এক মুহূর্ত আগে যেখানে মায়েরা বাচ্চাদের শীতল হাত ধরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলেন, পরের মুহূর্তেই ডাক্তাররা বাচ্চাগুলোর হাতে জীবন ভরে দিচ্ছিলেন। এটা শুধু অনুভব করা যায়।
একে একে যখন তারা শেষ বাচ্চাটার কাছে পৌঁছান, তখন প্রথম ইনজেকশন দেওয়া বাচ্চাদের কয়েকজন কোমা থেকে জেগে ওঠে। আর কেঁদে ওঠে তাদের বাবা মা, এবার আনন্দে। এটা শুধু প্রতিষেধক ছিলো না, ছিলো পুরো যুগান্তকারী সাফল্য। ইতিহাসের বাঁক বদলে দেওয়া ঘটনা।
সাফল্যের কথা ছড়িয়ে পড়ে, অসুস্থ বাচ্চাদের অভিভাবকরা হামলে পড়ে ওষুধের জন্য, কিন্তু এতো ওষুধ তো আর ছিল না। এই সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে আসে এলি লিলি কোম্পানি। তাদের সকল উপায় উপকরণ ঢেলে দেয় এতে। প্রথমে এক বছর লেগে যায় সবচেয়ে সুবিধাজনক প্রক্রিয়া বের করতেই। ১৯২২এর গ্রীষ্মে তারা পটেন্ট ইনসুলিন বাজারজাত করতে সমর্থ হয়।
১৯২২ এর এপ্রিল মাসে টরন্টোর দলটা ইনসুলিনের আবিষ্কার ও ব্যবহারের সাফল্য নিয়ে পেপার প্রকাশ করেন ‘দ্য ইফেক্টস প্রোডিউসড অন ডায়াবেটিক বাই এক্সট্রাক্টস অব প্যানক্রিয়াস’ শিরোনামে। এই পেপারেই তারা প্রথম ইনসুলিন শব্দ ব্যবহার করেন।
এই কৃতিত্বের জন্য ১৯২৩ সালে ব্যানটিং ও ম্যাকলেয়ডকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বেস্টের পরিবর্তে ম্যাকলেয়ড নোবেল পাওয়ায় প্রচণ্ড ক্ষেপে যান ব্যানটিং এবং নোবেল নিতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু বন্ধুরা তাকে এই বলে রাজি করান যে, প্রথম কানাডিয়ান হিসেবে পুরস্কার না নেওয়াটা বোকামি হবে। তিনিই চিকিৎসা বিজ্ঞানে সবচেয়ে কম বয়সী নোবেল বিজয়ী। পরে উনি পুরস্কারের টাকা ভাগ করে নেন বেস্টের সাথে। ম্যাকলেয়ডও তার ভাগ দেন কলিপকে।
ব্যানটিং, কলিপ ও বেস্ট তাদের আবিষ্কারের পেটেন্ট টরন্টো ইউনিভার্সিটির কাছে বিক্রি করে দেন প্রত্যেকে মাত্র ১ ডলারের বিনিময়ে। এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে ব্যানটিং তার বিখ্যাত উক্তিটা করেন- ‘ইনসুলিন বিলংস ট দ্য ওয়ার্ল্ড, নট টু মি’।
বাস্তবে ইনসুলিন আবিষ্কার তাই শুধু ব্যানটিং, বেস্ট বা ম্যাকলেয়ড কলিপের রেষারেষির ঘটনা না। বাস্তবতা হলো ইনসুলিন ওই সময় ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য কী করেছিল সেটা। সেটা যতই ভাবা যায়, এই মহত্তম আবিষ্কারটা ততোই বড় হয়ে ধরা দেয়।
(গরু ও শুকরের অগ্ন্যাশয় থেকে আহরিত ইনসুলিন ব্যবহৃত হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। তবে এতে এলার্জি হতো অনেকেরই। ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে সরাসরি মানুষের জিন থেকে ইনসুলিন তৈরি শুরু হয় ১৯৭৮ সালে।)
এএইচএস